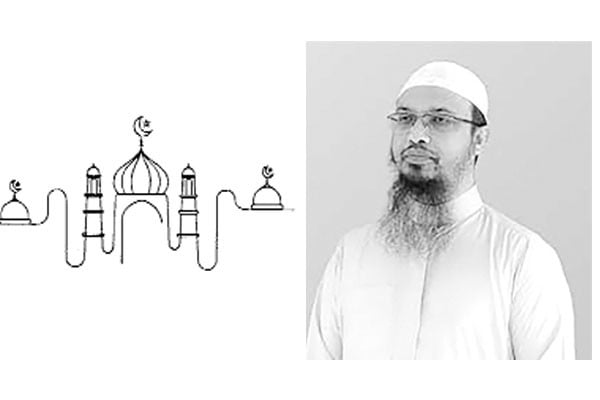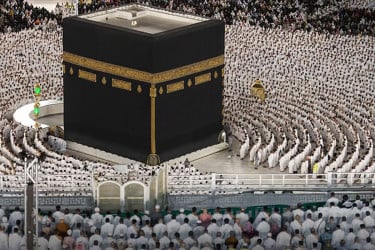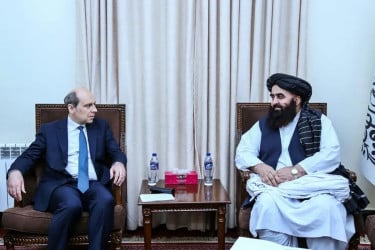‘কফি হাউসের সেই আড্ডাটা আজ আর নেই’। প্রয়াত কণ্ঠশিল্পী মান্না দের এ গানটি শুনলে স্মৃতিকাতর হন না, এমন কেউ আছেন বলে মনে হয় না। জীবনের কোনো না কোনো সময় বন্ধুবান্ধব, স্বজন-সুহৃদদের সঙ্গে যারা আড্ডায় মেতেছেন, তাদের মনের পর্দায় ভেসে ওঠে স্মৃতিময় সেসব চিত্র। সে পর্দায় জীবন্ত হয়ে ওঠে কতগুলো চেনা মুখ, যাদের কেউ হয়তো ইহজগৎ থেকে বিদায় নিয়েছেন, কেউবা হয়েছেন পরবাসী। কারও কারও সঙ্গে দেখা হয় না বছরের পর বছর। তারপরও স্মৃতির আয়নায় রয়েছে তাদের উজ্জ্বল উপস্থিতি। অবশ্য বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তির সময়ে হারিয়ে যাওয়া অনেক বন্ধু-স্বজনের সন্ধান-সাক্ষাৎ মেলে ফেসবুক-মোহনায়।
ছাত্রজীবন বা কর্মজীবন হোক, বন্ধু-সহকর্মীদের সঙ্গে আড্ডা দেননি এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। তবে সময়ের সঙ্গে যেমন মানুষের জীবনের গতিপথ বদলায়, তেমনি আড্ডাস্থল ও অংশীজনরাও বদলে যায়। অন্যের কথা বলে লাভ নেই, নিজের অভিজ্ঞতার কথাই বলি। মধ্য ষাট পেরিয়ে যাওয়া জীবনে বেশ কয়েকবার আড্ডার ধরন ও সঙ্গীদের পরিবর্তন হয়েছে। ছেলেবেলায় গ্রামে যাদের সঙ্গে আড্ডা দিতাম, পরবর্তী জীবনে সেভাবে আর একত্র হতে পারিনি। শৈশবে আমাদের আড্ডাস্থল ছিল গ্রামের ছোট্ট খেলার মাঠের এক কোণে অথবা কারও বাড়ির বড় কোনো বৃক্ষতলে। অলস দুপুর গাছের ছায়ায় কিংবা খেলাধুলা শেষে পড়ন্ত বিকাল থেকে সন্ধ্যার পর পর্যন্ত মাঠের সেই নির্মল আড্ডার কথা মনে হলে স্মৃতিকাতর হয়ে পড়ি। সেসব আড্ডায় নির্দিষ্ট কোনো আলোচ্যসূচি থাকত না। যখন শ্রীনগর হাইস্কুলে পড়তাম, তখন ক্লাস শুরুর আগে এবং টিফিন পিরিয়ডে আড্ডা জমত স্কুল চত্বরসংলগ্ন বিশাল দিঘির ঘাটলায়। সেখানে ছিল একটি শতবর্ষী বকুল গাছ। আমরা জায়গাটির নাম দিয়েছিলাম ‘বকুলতলা’। আর যখন শ্রীনগর কলেজে পড়ি, তখন আড্ডা হতো কলেজ শহীদ মিনারের পাদদেশে আম গাছের ছায়াতলে। সেসব আড্ডায় লেখাপড়া, সমাজ-সংস্কৃতি, নাটক-সিনেমা এবং রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ বিষয় হিসেবে স্থান পেত। সবই চলত অত্যন্ত সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশে, খোলামনে। মতান্তর ছিল নিত্যনৈমিত্তিক, তবে মনান্তর হয়নি কখনোই। ওই সময় আমাদের আরেকটি আড্ডাস্থল ছিল শ্রীনগর বাজারের চকবাজারে শংকরদার সেলুন। ক্লাস টেন পর্যন্ত পড়াশোনা করা শংকরদা পৈতৃক পেশাকেই বেছে নিয়েছিলেন জীবিকা নির্বাহের অবলম্বন হিসেবে। আশি দশকের মাঝামাঝি সময়ে তিনি চলে যান ভারতের পশ্চিমবঙ্গে। তিনি চলে যাওয়ার পর তার শিস্য নিতাই সেলুনটি চালাত, এখনো চালু রেখেছে। শ্রীনগরে গেলে নিতাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়। কিন্তু ওর সেলুনে বসে আড্ডা দেওয়া হয় না। একা কি আড্ডা দেওয়া যায়? একসময়ের আড্ডার অংশীজন-বন্ধুরা জীবন-নদীর খরস্র্রোতে একেকজন একেক দিকে ভেসে গেছি। কারও কারও সঙ্গে কালেভদ্রে দেখা হয়। যোগাযোগ হয় সেলফোনে।
এইচএসসির পাট চুকিয়ে ঢাকায় আসি ১৯৭৭ সালে। বড় ভাই বাসা নেন নারিন্দার ভজহরি সাহা স্ট্রিটে। এলাকাটি ‘ভূতের গলি’ নামে পরিচিত। ঢাকায় অবশ্য আরেকটি ভূতের গলি আছে ধানমন্ডির হাতিরপুলে। ঢাকায় আসার পর নতুন কিছু বন্ধুবান্ধব জোটে। আমাদের বাসাটির উল্টো দিকে একটি অর্পিত সম্পত্তির বাড়িতে বসবাস করত কয়েকটি পরিবার। তারা সবাই নোয়াখালীর বসিন্দা, পরস্পর আত্মীয়। আশপাশের সবাই তাই ওটাকে বলত ‘নোয়াখাইল্লা বাড়ি’। বাড়িটি লিজ নিয়ে তারা বসবাস করত। এখনো সেই পুরোনো অবয়বেই আছে বাড়িটি। সেই বাড়ির সামনে একটু খোলা চত্বর ছিল, অবসরে আমরা সেখানে বসতাম। আগে ঢাকায় বেশির ভাগ আবাসিক বাড়ি ছিল দোতলা, বড়জোর তিনতলা। বাণিজ্যিক ভবন পাঁচ-ছয়তলা হতো। বহুতল আবাসিক ভবনের কালচার তখনো শুরু হযনি। তখন ঢাকা শহর বিভিন্ন মহল্লায় বিভক্ত ছিল। বহুতল আবাসিক ভবন চালু হওয়ার পর মহল্লা এখন অপস্রিয়মাণ। আগে মহল্লার প্রতিবেশীদের মধ্যে যে হৃদ্যতা-আন্তরিকতার সম্পর্ক ছিল এখনকার অ্যাপার্টমেন্ট ভবনে তা নেই। কেউ কারও খবর রাখে না। সবাই যেন বিচ্ছিন্ন দ্বীপ। আগে প্রতিটি বাড়ির সামনে একফালি খোলা বরান্দা থাকত, যা ‘রোয়াক’ নামে পরিচিত। পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় বলে ‘রক’। পাড়া-মহল্লার কিশোর-তরুণ-যুবকরা সেসব রোয়াক বা রকে বসে আড্ডা দিত। কেউ কেউ মস্তানিও যে করত না, তা-ও নয়। তবে তারা হালজমানার সন্ত্রাসীদের মতো ছিল না। তাদের অস্ত্র ছিল চেলাকাঠ, হকিস্টিক, বড়জোর ডেগার, মানে চাকু। আজকালকার মতো হাতে হাতে আগ্নেয়াস্ত্র ছিল না। রকে বসা মস্তানদের কলকাতায় বলা হতো ‘রকবাজ’। স্বাধীনতার পর তারই অপভ্রংশ হিসেবে আমাদের দেশে ‘রংবাজ’ শব্দটি চালু হয়।
রকে বসে আড্ডা দেওয়া ও তাকে কেন্দ্র করে ছোটখাটো বাহিনী গড়ে ওঠার চিত্র নিপুণভবে এঁকেছেন জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক ও পরিচালক হুমায়ূন আহমেদ তাঁর ‘কোথাও কেউ নেই’ ধারাবাহিক নাটকে। সেই নাটকের ‘বাকের ভাই’ চরিত্রটি ছিল তেমনি এক রকবাজ তথা রংবাজের প্রতিচ্ছবি। প্রতিটি পাড়া-মহল্লায় এমন গ্রুপ থাকত। তবে এসব গ্রুপ কোনো বড় ধরনের অপরাধ করত না। বরং মহল্লায় কোনো অপরাধ যাতে সংঘটিত না হয়, সেদিকে নজর রেখে তা প্রতিরাধে তৎপর থাকত।
ভূতের গলিতে মন্টুদের বাড়ির রকে আমরা যারা বসতাম, তারা অবশ্য অমন কোনো গ্রুপ গড়ার চিন্তা করিনি। শ্রেফ সময় কাটানোর জন্য নির্মল আড্ডা দেওয়াই ছিল উদ্দেশ্য। আমরা কথাবার্তা, আচরণে এতটাই সংযত থাকতাম যে আশপাশের মুরব্বিরা কখনোই আপত্তি তোলেননি। মাঝেমধ্যে মন্টুর আব্বা মসজিদে আসর নামাজ পড়তে যাওয়ার সময় শুধু বলতেন, ‘মিয়ারা খালি গপ্পো কইর না, নামাজ পইড়।’ মন্টু ছাড়াও সে আসরে নিয়মিত সদস্য ছিল মতি, স্বপন, পাপ্পু। মাঝেমধ্যে রাজার দেউড়ি থেকে এসে শরিক হতো বন্ধু হাদী। কয়েক বছর আগে সে না-ফেরার জগতের বাসিন্দা হয়েছে। স্বপনের পিতা এলাকায় পরিচিত ছিলেন ‘বদু মেম্বার’ হিসেবে। তাঁর নাম ছিল বদরুদ্দিন। দাপুটে এবং রাগী মানুষ ছিলেন তিনি। সবাই তাঁকে সমীহ করত। ঢাকা পৌরসভা কিংবা পঞ্চায়েত কমিটির মেম্বার ছিলেন একসময়। আমাকে খুব স্নেহ করতেন। ভজহরি সাহা স্ট্রিট ও নারিন্দা রোডের সংযোগস্থলে তাঁর ‘হোটেল মেসবাহ্’ নামে একটি হোটেল কাম রেস্তোরাঁ ছিল। বৃষ্টিবাদলের দিনে আমরা বসতাম সে রেস্তোরাঁয়। তবে স্বপন আসত না। বাপকে ভীষণ ভয় পেত। বলত, ‘আমি হালায় বাঘের সামনে যাইবার পারুম, মগর বদু মিয়ার সামনে না।’ কখনো কখনো আমরা বসতাম টিপু সুলতান রোডের মাথায় (এখন যেখানে আবদুর রহিম কমিউনিটি সেন্টার) ‘সিঞ্জন সাংস্কৃতিক সংসদ’ অফিসে। সংগঠনটি এখন আছে কি না, জানি না। বন্ধু ফখরুল ইসলাম মন্টু জাপানে স্থায়ী নিবাস গেড়েছে, স্বপন অসুস্থ, মতি আছে ঢাকাতেই। কেউ কারও সঙ্গে আর আগের মতো সম্পর্কিত নেই।
এর কয়েক বছর পর বেসরকারি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে চাকরি নেই। আমার আবাসস্থল হয় ইসলামপুরের কুমারটুলির একটি মেসবাড়ি। নবাব আমলের পুরোনো বিল্ডিং, এই পড়ে কি সেই পড়ে অবস্থা। দোতলা ভবনটির নিচে গফুর সাহেবের প্রেস ও অফিস। পরিত্যক্ত এ বাড়িটির অলিখিত মালিক ছিলেন তিনিই। দেখভাল তিনিই করেন। চাচাত ভাই হাসানের মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে পরিচয়। তাঁর অফিসে মাঝেমধ্যে আমরা গল্পে বসতাম। দেশে তখন এরশাদের সামরিক শাসন চলছে। বিএনপির কর্মী হিসেবে মিছিল-মিটিংয়ে যাই, হরতালে পিকেটিংয়ে বেরোই। পুলিশের ধাওয়া খেয়ে আশ্রয় নিই গফুর ভাইয়ের অফিসে। কারফিউ হলে বসে থাকি মেসের ঘরে। তখন জম্পেশ আড্ডা হয় নানা বিষয়ে। মেস-মুরব্বি খোকা কাকা শোনাতেন তাঁর আসাম থাকাকালীন নানা ঘটনার গল্প। আমরা মজা পাই। কখনো আড়ালে-আবডালে টিপ্পনী কাটি। এভাবেই চলে দিন। লেখালেখির সুবাদে যাতায়াত দৈনিক দেশ, দৈনিক বাংলা, সংবাদ অফিসে। তবে দৈনিক দেশেই সময় কাটাতাম বেশি। পত্রিকাটির শ্রীনগর প্রতিনিধি ছিলাম তখন। সম্পাদক ছিলেন খ্যাতিমান সাংবাদিক সানাউল্লাহ নূরী। নজরুল গবেষক শেখ নূরুল ইসলাম ছিলেন অন্যতম সহকারী সম্পাদক। এলাকার ছেলে হিসেবে বিশেষ স্নেহ করতেন। মূলত সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয় লেখার তালিম আমাকে তিনিই দিয়েছেন। ২০০৫ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন। দৈনিক দেশ অফিসের সম্পাদকীয় বিভাগের কক্ষে সিনিয়রদের আড্ডা হতো। মুনশী আবদুল মান্নান, কবি মাহবুব হাসান, আনোয়ারুল হক, রফিকুল ইসলাম, শহীদুল হক খান (চলচ্চিত্র পরিচালক) প্রমুখ সে আসর জমাতেন। জুনিয়র আমি ছিলাম প্রধানত শ্রোতা সে আসরের।
কয়েক বছর আগে সিনিয়রদের তেমনি এক আসরে প্রবেশাধিকার পেয়েছিলাম। আমার সাবেক বস, সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার প্রেস সচিব তাজুল ইসলামের সুবাদে সে আড্ডায় অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছিলাম। আসর বসত ধানমন্ডিতে নজরুল ইনস্টিটিউটের পাশে সাবেক সচিব আবদুল হান্নানের বাসায়। পেশাগত জীবনের শুরুতে সাংবাদিকতা ও কলেজে শিক্ষকতা করা এই সাবেক আমলা ছিলেন অত্যন্ত অভিজ্ঞ একজন জ্ঞানী মানুষ। প্রতি শনিবার তাঁরা সমবেত হতেন। তাই নাম দিয়েছিলেন ‘শনির আড্ডা’। যদিও কোনো শনি তাঁরা ঘটাননি বা ঘটানোর চেষ্টাও করেননি। আসরের মধ্যমণি ছিলেন ইয়াসিন আমিন ভাই। তিনি প্রখ্যাত সংবাদিক ও লেখক-গবেষক সৈয়দ আবুল মকসুদের সম্বন্ধী। আসতেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সাবেক ডিজি ওয়ালিউর রহমান আপেল, সাপ্তাহিক হলিডের সহকারী সম্পাদক ফখরুদ্দিন আহমদ, উন্নয়ন কর্মী আবুল বশর প্রমুখ। সে আড্ডাটি এখন আর বসে না। হান্নান সাহেব, ইয়াসিন ভাই, ফখরুদ্দিন ভাইয়ের ইন্তেকালের পর শনির আড্ডা ভেঙে গেছে।
বাঙালির আটপৌরে জীবনে আড্ডা একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। কাজের অবসরে ক্লান্তি দূর করতে আড্ডার মতো ধন্বন্তরি আর কিছু আছে বলে মনে হয় না। সারা দিনের কর্মক্লান্ত মানুষটি বন্ধু বা স্বজনদের সঙ্গে আড্ডায় শামিল হতে পারলে মুহূর্তেই ঝরঝরে হয়ে ওঠে। আমরা বন্ধুরা আড্ডাকে বলতাম একঘেয়েমি কাটানোর ‘টনিক’। এখন আর কোনো আড্ডায় নিয়মিত বসা হয় না। বন্ধুবান্ধবের সংখ্যাও কমে এসেছে। নিয়মিত গ্রামে যাই, কিন্তু আড্ডা দেওয়ার মতো লোক পাই না। এখন দুই-পাঁচজন মানুষ একসঙ্গে হলে দুই কথার পরেই তা হয়ে ওঠে রাজনৈতিক বিতর্ক সভা। নির্মল আড্ডা যাকে বলে, তা যেন উধাও হয়ে গেছে। যান্ত্রিক সময়ে মানুষও হয়ে উঠেছে যান্ত্রিক। অলস আড্ডায় সময় ব্যয় না করে বিত্ত-বেসাত বৃদ্ধির পেছনে সময় ব্যয় করাকেই তারা শ্রেয় মনে করে।
আড্ডার জন্য যখন মন আঁকুপাঁকু করে তখনই অবচেতন মনে কবিগুরুর গান শুনতে পাই- ‘পুরানো সেই দিনের কথা ভুলবি কি রে হায়/ ও সেই চোখে দেখা প্রাণের কথা, সে কি ভোলা যায়/ আয় আর একটিবার আয় রে সখা প্রাণের মাঝে আয়/ মোরা সুখের দুঃখের কথা কব, প্রাণ জুড়াবে তায়...’। নির্মম সত্যি হলো, পুরোনো সেই দিন আর ফিরে আসবে না, সুখ-দুঃখের কথাও কেউ শুনতে চায় না। সবাই এখন নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত।
লেখক : সাংবাদিক ও রাজনীতি বিশ্লেষক