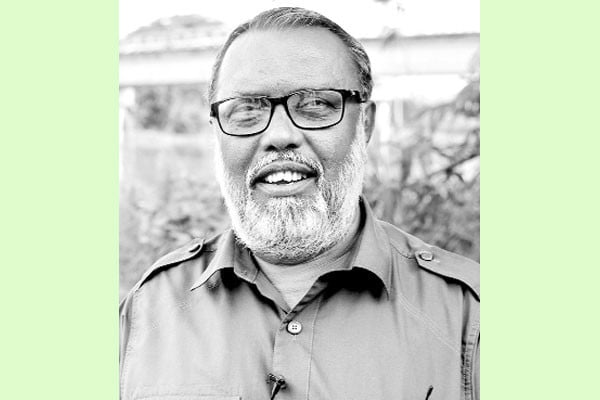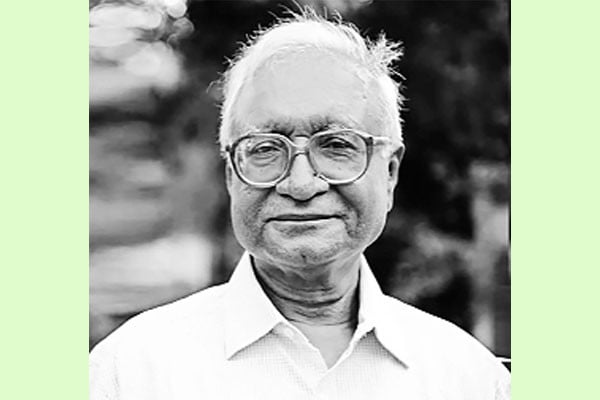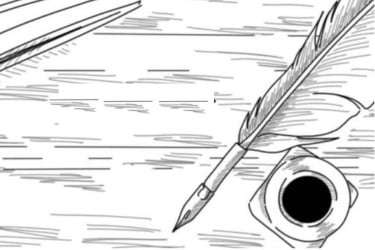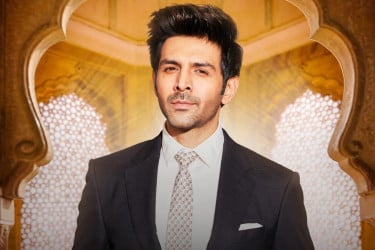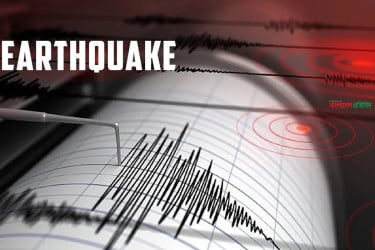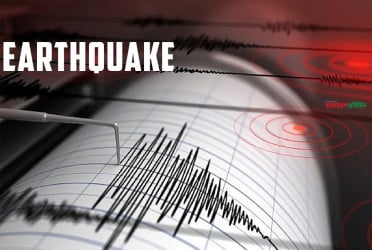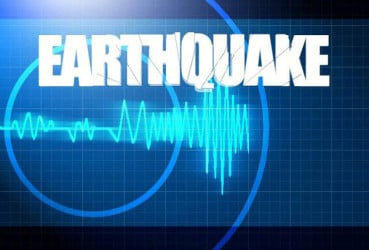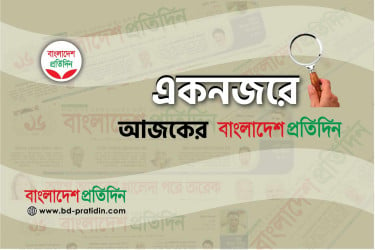বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, নদীভাঙন কিংবা খরার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ নতুন কিছু নয়। এসব দুর্যোগের সঙ্গে লড়াই করতে করতে দেশের মানুষ অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছে। কিন্তু ভূমিকম্প এক সম্পূর্ণ ভিন্ন বাস্তবতা-এটি সবচেয়ে অপ্রত্যাশিত, সবচেয়ে দ্রুত এবং প্রায়শই সবচেয়ে বিধ্বংসী দুর্যোগ। সতর্কতা বা পালানোর সময় নেই; কয়েক সেকেন্ডেই একটি শহরের ভাগ্য বদলে দিতে পারে।
২১ নভেম্বরের ভূমিকম্প আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছে- ঝুঁকি দূরে নয়, বরং দরজার সামনে দাঁড়িয়ে।
ভূমিকম্প-ঝুঁকির ভূগোল : বাংলাদেশ তিনটি সক্রিয় টেকটোনিক প্লেট- ভারতীয়, বার্মিজ ও ইউরেশীয় প্লেটের সংযোগস্থলের কাছে অবস্থিত। এ অবস্থানই দেশটিকে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম ভূমিকম্প-ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে পরিণত করেছে। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর জানায়- গত এক শতকে দেশে অন্তত ২০০টিরও বেশি ভূমিকম্প রেকর্ড হয়েছে। বছরে গড়ে ২৫-৩০টি ক্ষুদ্র কম্পন অনুভূত হয়, যার বেশির ভাগই সিলেট, চট্টগ্রাম, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে।
বিশেষজ্ঞদের মতে, সিলেটের নিচে থাকা ‘দাউকি ফল্ট’, চট্টগ্রাম-টেকনাফের ‘চিটাগং-আরাকান ফল্ট’ এবং মিয়ানমারের ‘সাগাইং ফল্ট’-এ তিনটি সক্রিয় ফল্ট জোন বাংলাদেশকে বড় ধরনের ভূমিকম্পের মুখে ফেলেছে।
ঢাকা : ভূমিকম্পের জন্য নির্মিত নয় : আন্তর্জাতিক সংস্থা জাপান আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা-জাইকা একাধিক গবেষণায় সতর্ক করেছে- ঢাকায় যদি ম্যাগনিচিউড ৭ দশমিক ৫ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানে, তবে রাজধানীর ৭০ শতাংশ ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ২ লাখেরও বেশি মানুষের প্রাণহানি ঘটতে পারে। আর্থিক ক্ষতি দাঁড়াতে পারে ৩ থেকে ৫ হাজার কোটি ডলার।
এ পূর্বাভাস কেবল অনুমানের ওপর ভিত্তি করে নয়- ঢাকার জনসংখ্যার ঘনত্ব, অপরিকল্পিত নগরায়ণ, অত্যধিক উচ্চ ভবন, অনিরাপদ নির্মাণ পদ্ধতি এবং সংকীর্ণ সড়ক- সব মিলিয়ে নগরটিকে একটি ‘উচ্চ-ঝুঁকির ভূমিকম্প-ফাঁদে’ পরিণত করেছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে রাজধানীতে ২০ তলা বা তার বেশি ভবনের সংখ্যা কয়েক গুণ বেড়েছে। কিন্তু এসব ভবনের বড় অংশেই দেখা যায়- বিল্ডিং কোড মানা হয়নি; সঠিক সয়েল টেস্ট করা হয়নি; নিম্নমানের উপকরণ ব্যবহৃত হয়েছে; তদারকি দুর্বল; আশপাশের সড়ক অতি সংকীর্ণ হওয়ার ফলে ভূমিকম্পের সময় উদ্ধার কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হওয়া অনিবার্য।
সম্ভাব্য অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের চিত্র আরও ভয়াবহ : একটি বড় ভূমিকম্প শুধু প্রাণহানি নয়- বাংলাদেশের অর্থনীতির মেরুদন্ডকে ভেঙে দিতে পারে। সংশ্লিষ্টদের হিসাবে-মোট অর্থনৈতিক ক্ষতি হতে পারে ৩ থেকে ৫ লাখ কোটি টাকা, যা বাংলাদেশের জিডিপির ১০-১৫ শতাংশ। সেতু, হাসপাতাল, স্কুল, ফ্লাইওভার, সরকারি ভবন- সব মিলিয়ে হাজার হাজার কোটি টাকার স্থাপনা ঝুঁকিতে। গ্যাস, পানি, বিদ্যুৎ সরবরাহ ভেঙে পড়লে রাজধানী কার্যত অচল হয়ে যাবে। গার্মেন্টস শিল্প স্থবির হলে রপ্তানি খাতে ধস নামবে। ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণ বেড়ে যাবে, কারণ অসংখ্য মানুষ ও প্রতিষ্ঠান তাদের সম্পদ হারাবে। বিমা শিল্প বর্তমানে বড় ধরনের বিপর্যয় মোকাবিলার সক্ষমতা রাখে না। এক কথায়, একটি বড় ভূমিকম্প হলে বাংলাদেশকে বহু বছর পিছিয়ে যেতে হবে।
প্রতিরোধ নয়- ক্ষতি কমানোই মূল লক্ষ্য : ভূমিকম্প প্রতিরোধের কোনো উপায় নেই। কিন্তু সঠিক নীতি, বিজ্ঞানভিত্তিক পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি থাকলে ক্ষতি অনেকটাই কমানো সম্ভব। এর জন্য সরকারের সক্রিয় নেতৃত্ব এবং সংশ্লিষ্ট সব প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত উদ্যোগ জরুরি।
সরকারকে এখন যে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত : বাংলাদেশ জাতীয় বিল্ডিং কোড কঠোরভাবে বাস্তবায়ন। বাংলাদেশ জাতীয় বিল্ডিং কোড শুধু কাগজে থাকা আইন নয়- এটাই জীবনরক্ষাকারী নকশা। কিন্তু বাস্তবে এর প্রয়োগ অত্যন্ত দুর্বল। রাজউক, সিটি করপোরেশন, পৌরসভা- সব প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন প্রক্রিয়া ডিজিটাল ও স্বচ্ছ করতে হবে।
অবৈধ ও ঝুঁকিপূর্ণ ভবনের তালিকা প্রকাশ এবং রেট্রোফিটিং প্রক্রিয়া দ্রুত শুরু করা।
উচ্চঝুঁকির ভবনগুলো পুনর্মূল্যায়ন : ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেটের পুরোনো স্কুল, হাসপাতাল, সরকারি অফিস, বাজার, অ্যাপার্টমেন্টগুলো অতি ঝুঁকিপূর্ণ। এসব স্থাপনা আবার পরীক্ষা করা, দুর্বল অংশগুলো শক্তিশালী করা এবং প্রয়োজনে ভেঙে পুনর্নিমাণ করা জরুরি।
সিসমিক স্টেশন ও গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন : বাংলাদেশে বর্তমানে সিসমিক মনিটরিং স্টেশনের সংখ্যা খুবই কম। ভূমিকম্পের পূর্বাভাস ও বিশ্লেষণ উন্নত করতে- অন্তত ৫০টির বেশি আধুনিক সিসমিক স্টেশন দরকার। ভূ-প্রযুক্তি গবেষণাগার, জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সিস্টেম ও আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স-ভিত্তিক রিস্ক মডেল স্থাপন করা প্রয়োজন।
উদ্ধার ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বিপ্লব : ফায়ার সার্ভিসকে আধুনিক যন্ত্রপাতি; সেনাবাহিনী ও সিভিল ডিফেন্সকে উন্নত রেসকিউ সরঞ্জাম; জরুরি চিকিৎসা টিম বৃদ্ধি; ভবনধসে আটক মানুষ শনাক্তে ড্রোন ও থার্মাল স্ক্যানার ব্যবহারের প্রশিক্ষণ ও জরুরি উদ্ধার ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করতে হবে।
স্কুল-কলেজ-অফিসে নিয়মিত মহড়া বাধ্যতামূলক : জাপানের মতো দেশে বছরে ৩-৪ বার মহড়া হয়। সেখানে একটি শিশু জানে-ভূমিকম্প হলে তার প্রথম করণীয় কী। বাংলাদেশেও একই ধরনের শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে।
রিয়েল এস্টেট খাতের দায়িত্ব : নিরাপদ নগরায়ণ শুধু সরকারের দায়িত্ব নয়; রিয়েল এস্টেট খাতও এখানে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। তাদের পালন করতে হবে বিল্ডিং কোড অনুযায়ী নকশা; সঠিক সয়েল টেস্ট; মানসম্মত রড-সিমেন্ট-ইট ব্যবহার; প্রকৌশলীর তদারকি ও ক্রেতাকে স্বচ্ছ তথ্য প্রদান। সব সময়ে মনে রাখতে হবে ঝুঁকিপূর্ণ ভবন বিক্রি করা শুধু অনৈতিক নয়- এটি অপরাধ।
জাপানের সফলতা এবং বাংলাদেশের শিক্ষণীয় : জাপান পৃথিবীর সবচেয়ে ভূমিকম্প-প্রবণ দেশগুলোর একটি, কিন্তু সেখানে ক্ষয়ক্ষতি তুলনামূলক কম। কারণ- অত্যাধুনিক বিল্ডিং কোড; আগে পুর্বাভাস দেওয়া; উন্নত গবেষণা অবকাঠামো; স্কুলে ভূমিকম্প শিক্ষা; উদ্ধার দলের উচ্চমানের প্রস্তুতি; ভূমিকম্প-সহনশীল নগর পরিকল্পনা। বাংলাদেশ যদি এই পথ অনুসরণ করে- ক্ষতি ৫০ শতাংশ পর্যন্ত কমানো সম্ভব।
এখনই সিদ্ধান্ত নিতে হবে : ভূমিকম্প বাংলাদেশের জন্য কোনো তাত্ত্বিক ঝুঁকি নয়- এটি বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত বাস্তবতা। একটি মাত্র বড় ভূমিকম্পে উন্নয়ন, অবকাঠামো, অর্থনীতি- সব কিছু ভেঙে পড়তে পারে।
রাষ্ট্র, আবাসন খাত এবং জনগণ- এই তিন স্তম্ভ শক্তিশালী হলেই আমরা নিরাপদ হতে পারব।
অন্যথায় প্রশ্নটি খুবই কঠিন কিন্তু সত্য- আমরা কি প্রস্তুত হয়ে বাঁচব, নাকি উদাসীনতায় বড় বিপর্যয়ের অপেক্ষা করব?
লেখক : ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জেসিএক্স ডেভেলপমেন্টস লিমিটেড