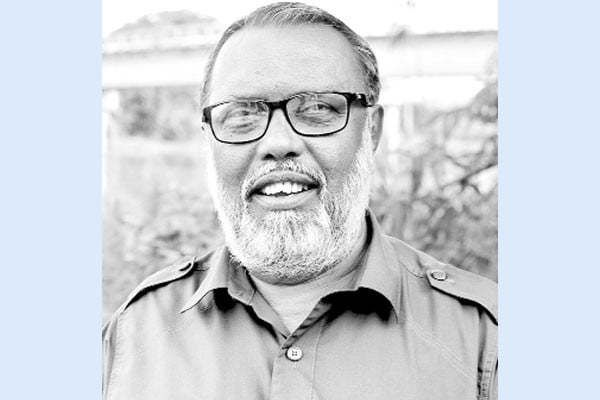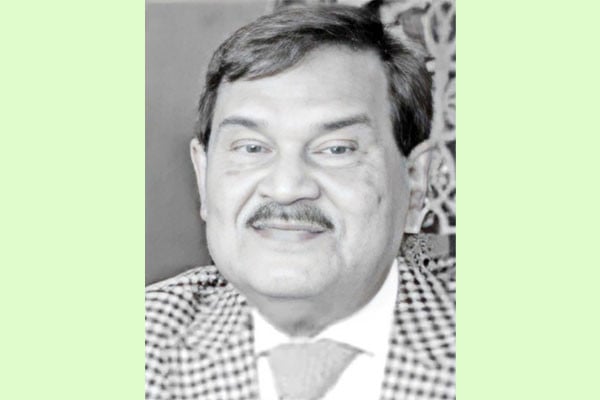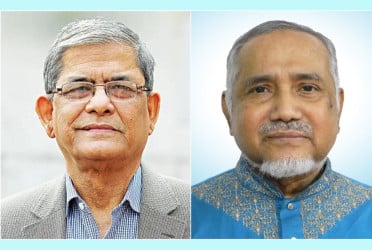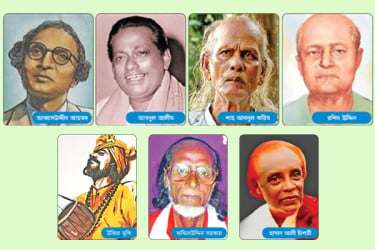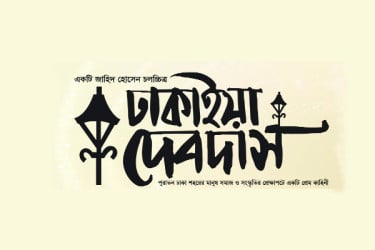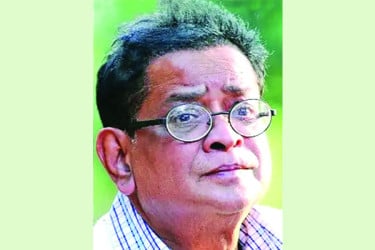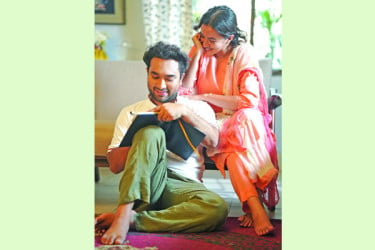স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ মূলত কৃষিনির্ভর অর্থনীতির দেশ ছিল। পরে শিল্প ও বাণিজ্যের বিস্তারে অর্থনীতির চাকা ঘুরতে শুরু করলেও মানুষের জীবনের প্রধান অবলম্বন খাদ্যের জোগান আজও কৃষকের ঘামে ভিজে আসে। গত ৫০ বছরে কৃষি ও কৃষকের চেহারা আমূল বদলে গেছে। আশির দশকে যখন বাংলাদেশ টেলিভিশনের কৃষি অনুষ্ঠান নির্মাণে যুক্ত হলাম, তখন থেকেই খুব কাছ থেকে কৃষির এই পরিবর্তনের সাক্ষী আমি। খাবারের প্লেটেই বোঝা যায় এই পরিবর্তন। আশি দশকের গ্রামের গৃহস্থের খাবার বলতে ছিল ভাত, এক কোণে সামান্য পিঁয়াজ আর একটি কাঁচা মরিচ। ধান-পাট ছাড়া কৃষকের আর কোনো আবাদ ছিল না। উঠোনের লাউ বা শিম গাছই রান্নার সবজির ভরসা। দিনে যতটুকু সবজি দরকার, তার সিকিভাগও মিটত না। মাছ চাষের কথা বললে অনেকে অবাক হয়ে তাকাতেন, ‘মাছ আবার চাষ হয় নাকি? মাছ তো বিলঝিলেই মেলে!’ অথচ বাড়ির সামনের পুকুরটি থাকত পরিত্যক্ত, কেবল গোসল বা কাপড় ধোয়ার কাজে। সেই সময় থেকেই টেলিভিশনে সবজি চাষ, মাছ চাষ, মুরগি পালন নিয়ে নিরন্তর কথা বলে গেছি। টেলিভিশনে ‘হাকিম আলীর মৎস্য খামার’ প্রচারিত হওয়ার পর শিক্ষিত তরুণরা নেমে পড়েন মাছ চাষে, আর তাদের হাত ধরেই দেশে মাছ চাষে বিপ্লব ঘটে। উঠোনের সবজি চলে আসে ফসলের মাঠে। ফলে মানুষের প্লেটে ভাতের অংশ কমে, সেখানে যুক্ত হয় সবজি, মাছ, ডিম কিংবা মুরগির মাংস। ধীরে ধীরে খাদ্যাভ্যাসে আসে ফলও। অর্থাৎ কেবল পেট ভরানোর চিন্তা থেকে মানুষ এখন পুষ্টির কথাও ভাবছে। কিন্তু প্রশ্ন রয়ে যায়, ধান চাষ কি কৃষকের কাছ থেকে গুরুত্ব হারাচ্ছে?
মানিকগঞ্জের জয়মন্টপে গিয়ে দেখলাম মাঠের পর মাঠে আমন ধানের পাশে পেঁপে, পটোল, ঝিঙা, আগাম শিমের আবাদ। কৃষক আবু বক্কর সিদ্দিক সাত বিঘা জমিতে চাষ করেছেন পেঁপে। সার সার গাছে ফল ঝুলছে, গোড়া থেকে আগা পর্যন্ত। তিনি জানালেন, আগে এ জমিতে ধান চাষ করতেন, কিন্তু লাভ হতো না। পেঁপেতে খরচের তুলনায় লাভ নিশ্চিত। শরিফুল ইসলাম, হাফিজ উদ্দিন, রানা হোসেন, হাসেম আলীসহ অনেকেই এখন আর ধান চাষ করেন না, চাল কিনে খান। একই চিত্র সাভারেও। ধানের জমিতে এখন শাকসবজির আবাদ। চাষ হচ্ছে ফুলের। সারা দেশেই এরকম প্রবণতা। কৃষক জানেন ধান নয়, উচ্চমূল্যের ফলফসলই তার ভালো আয়ের পথ। পেঁপে, পেয়ারা, ড্রাগন ফল, মাল্টা, তরমুজ কিংবা ফুল চাষে কৃষকের মুখে হাসি ফুটেছে। প্রশ্ন জাগে, তাহলে আগামী দিনে ভাতের জোগান আসবে কোথা থেকে?
বাংলাদেশের কৃষি পাল্টে গেছে। স্বাধীনতার পর যেখানে ৮৫ শতাংশ মানুষ কৃষির ওপর নির্ভরশীল ছিল, সেখানে এখন সে হার ৪০ শতাংশের কাছাকাছি। ১৯৭২-৭৩ সালে জিডিপিতে কৃষির অবদান ছিল ৫৮ শতাংশ, ২০১৯-২০ সালে এসে তা নেমে আসে ১৩ শতাংশে। তবু সামগ্রিক উৎপাদন বেড়েছে প্রায় ছয় গুণ।
পরিসংখ্যান বলছে, দেশের আবাদি জমি ৮৫ লাখ হেক্টরের বেশি। এর মধ্যে এক ফসলি, দুই ফসলি, তিন ফসলি জমির ব্যবহারে এসেছে বৈচিত্র্য। তিন মৌসুমে ধান, বছরজুড়ে সবজি-ফল, সাথি ফসল, অন্তঃফসল, মিশ্র ফসল; সবকিছু মিলিয়ে জমির সর্বোত্তম ব্যবহার এখন চোখে পড়ে। যেখানে আগে চাষাবাদের কল্পনাই ছিল না, সেখানে এখন ড্রাগন ফল বা পেয়ারাবাগান। বরেন্দ্রের অনুর্বর জমিতে, দক্ষিণের জলমগ্ন এলাকায়, এমনকি ঘরের উঠোনেও চলছে মাছ চাষ।
বাগেরহাটের মোল্লাহাটের কথা অনেক শুনিয়েছি আপনাদের। সে এলাকার মানুষ না খেয়ে দিনাতিপাত করত। বছরের কয়েক মাস খেতে হতো ঢ্যাপের চালের ভাত। সেই এলাকাটি এখন থেকে ৩০ বছর আগেই চিংড়ি চাষে সাফল্যের জন্য খুলনার কুয়েত হিসেবে পরিচিতি অর্জন করে। এখন সেটি দক্ষিণের অন্যতম সমৃদ্ধ ও ধনী মানুষের এলাকা। দক্ষিণাঞ্চলের যশোরের কথা যদি বলি। গদখালি-পানিসারা গ্রামের মানুষ কৃষির কোনো ভবিষ্যৎ খুঁজে পেত না। এখন ওই এলাকাটি পরিণত হয়েছে বাংলাদেশের নেদারল্যান্ডসে। ফুলের এই স্বর্গরাজ্যকে ঘিরে আশপাশের বিস্তীর্ণ এলাকার আবাদি খেত চলে গেছে ফুল চাষে। এক টুকরো জমি এখন সোনার চেয়ে দামি। বাণিজ্যিক কৃষির যুগে কৃষক জেনে গেছে তাকে টিকে থাকতে হলে আর্থিক লাভের জায়গায় আপস করার সুযোগ নেই। দেশের হাওড়ে ফলছে সোনা ফসল। চরাঞ্চলে সবজি চাষের বিপ্লব ঘটে গেছে। দক্ষিণের জলমগ্ন এলাকাগুলোতে এখন কৃষি, মাছ চাষসহ বছরব্যাপী উৎপাদনমুখী করতে নেওয়া হয়েছে নানা উদ্যোগ।
একসময় বাংলাদেশ টেলিভিশনের মাটি ও মানুষ অনুষ্ঠানে বারবার বলেছি ধান ও পাট চাষই একমাত্র কৃষি নয়। কৃষি সামনে ফলফসলের আবাদ। কৃষি মানে উচ্চমূল্যের ফসল করে আর্থিক উন্নতি করার ব্যাপার। কৃষি মানে মাছ চাষ করে জীবনকে ঘুরিয়ে দেওয়ার প্রয়াস। কৃষি মানে পোলট্রি খামার গড়ে নিজের ভাগ্য উন্নয়নের পাশাপাশি বহু মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেওয়া। সেই গল্পগুলো এখন বাস্তবতা। এখন কৃষক বোঝে কৃষি মানে শুধু বেঁচে থাকার প্রয়াস নয়। কৃষি মানে বাণিজ্য। কৃষি মানে উন্নয়ন। কৃষি মানে পরিবর্তন। কৃষি মানে নিজ হাতে নিজের জীবনকে ওপরে তুলে ধরা। তাই কৃষি করতে গিয়ে আটঘাট বেঁধে নামে সবাই। সবখানে শুধু টাকার কৃষি। তাহলে খাদ্যের কৃষির কী হবে? প্রশ্নটি সহজ করে বললে, আমাদের প্রধান খাদ্য ধান আবাদ এখন যেখানে এসেছে, এখান থেকে আর কতদূর যেতে পারবে?
স্বাধীনতার পর ১৯৭১-৭২ সালে ধানের মোট আবাদ ছিল ১ কোটি ৫১ লাখ হেক্টর, উৎপাদন মাত্র ৯৭ লাখ টন। ৪০ বছর পর আবাদ কমে দাঁড়াল প্রায় ১ কোটি ১৫ লাখ হেক্টরে, কিন্তু উৎপাদন বেড়ে দাঁড়াল সাড়ে তিন কোটি টনের বেশি। অর্থাৎ জমি কমলেও ফলন প্রায় আড়াই গুণ বেড়েছে। ২০১৯-২০ সালে উৎপাদন দাঁড়িয়েছে প্রায় ৪ কোটি টনে। আধুনিক জাত, উন্নত চাষাবাদ কৌশল ও গবেষণা-প্রচেষ্টার সমন্বয়েই এ সাফল্য সম্ভব হয়েছে।
এদিকে সবজি ও ফল উৎপাদনও আশ্চর্যজনক হারে বেড়েছে। গত ১৫ বছরে সবজি উৎপাদন প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। ফল চাষে এসেছে বিপ্লব। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পুষ্টি নিরাপত্তার বিষয়টি। মাছ চাষেও বাংলাদেশ এখন বিশ্বে সাফল্যের দৃষ্টান্ত। একসময়কার পতিত জমি, পুকুর-দিঘি, নদীনালা, বিল-বাঁওড় সব জায়গায়ই মাছ চাষ হচ্ছে। তিন দশকে মাছ উৎপাদন বেড়েছে ২৫ গুণ। বিশ্বে স্বাদু পানির উন্মুক্ত জলাশয় থেকে মাছ আহরণে বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয়। তবে এ সাফল্যের মাঝেও প্রশ্ন রয়ে গেছে, আমরা কি খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার পাশাপাশি আমদানির ওপর নির্ভরশীল হচ্ছি না? ২০২০-২১ অর্থবছরে চাল আমদানির জন্য খোলা হয়েছে প্রায় ৮৭ কোটি ডলারের এলসি। খাদ্যে স্বয়ম্ভরতার দাবি তুললেও আমদানির এ প্রবণতা আমাদের নিরাপত্তাকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে।
একই কৃষি, কখনো খাদ্যের উপলক্ষ্য, কখনো বাণিজ্যের। কখনো রপ্তানির উপলক্ষ্য, কখনো কর্মসংস্থানের। কখনো ব্যক্তি সাফল্যের, কখনো সামাজিক দায়বদ্ধতার, কখনো এটি শিল্পকারখানার মতো চুলচেরা হিসেবে উৎপাদনমুখী, কখনো প্রতিটি পদক্ষেপে ঝুঁঁকিপূর্ণ এক অনিশ্চয়তার ক্ষেত্র।
এ সামগ্রিক চিন্তায় কৃষি উৎপাদন, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও বাণিজ্যের দৌড়ে উদ্যোক্তা কৃষকের আর্থিক উন্নতি এবং সবশেষে দরিদ্র ভূমিহীন কৃষকের টিকে থাকার বিষয়গুলোতে আমরা সুষম দৃষ্টি রাখতে পারছি কি না, আজকের দিনে বড় প্রশ্ন। তবু আশার জায়গা আছে। আমাদের মাটি অনন্য, উর্বর। এখানে বীজ বপন করলে ফসল হয়, স্বপ্ন দেখলে বাস্তব রূপ নেয়। তাই আমাদের কৃষিকে সমন্বিতভাবে এগোতে হবে ধানের নিরাপত্তা, পুষ্টির নিশ্চয়তা এবং বাণিজ্যিক কৃষির বিকাশ সব একসঙ্গে নিয়ে।
অতএব কৃষির এই দীর্ঘ যাত্রাপথে আমরা দেখতে পাই সংগ্রাম, পরিবর্তন আর সাফল্যের এক অনন্য ইতিহাস। কৃষকই বাংলাদেশের মাটির প্রাণ, তাদের হাতেই ধরা থাকে খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ভবিষ্যৎ। কৃষি এখন বহুমুখী সম্ভাবনার ক্ষেত্র, যেখানে ফলন বাড়ানোর পাশাপাশি বৈচিত্র্য, উদ্ভাবন ও বাণিজ্যিক মূল্য যোগ হচ্ছে প্রতিনিয়ত। তবে এ পথচলায় ভারসাম্য রক্ষা করাই বড় চ্যালেঞ্জ। ধান, মাছ, সবজি, ফল কিংবা ফুল; সবকিছুর মধ্যেই টিকে থাকতে হবে টেকসই উৎপাদনের ধারণা। খাদ্যের নিশ্চয়তা, কৃষকের আয়, বাজারব্যবস্থাপনা, পরিবেশসহ সবকিছুর সমন্বয় ঘটিয়ে সামনে এগোতে হবে। আমরা যদি কৃষিকে উন্নয়ন, রপ্তানি, কর্মসংস্থান ও আত্মমর্যাদার হাতিয়ার হিসেবে দেখি, তবে কৃষি হবে আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি। বাংলাদেশের কৃষি আজ স্বপ্নের দুয়ারে দাঁড়িয়ে। আমাদের কৃষক জানেন ‘কৃষি মানেই উন্নয়ন, কৃষি মানেই পরিবর্তন।’ এখন প্রয়োজন নীতি, গবেষণা, প্রযুক্তি ও বাজারব্যবস্থাপনার সঠিক সমন্বয়। তাহলেই কৃষির ভবিষ্যৎ হবে টেকসই, আর কৃষকের স্বপ্ন হবে বাংলাদেশ নামের এ সবুজ ভূখণ্ডে সবচেয়ে বড় বাস্তবতা।
লেখক : মিডিয়াব্যক্তিত্ব