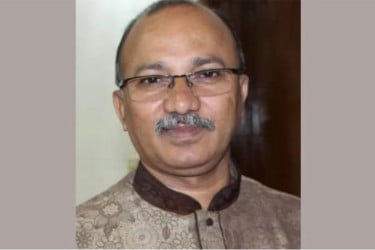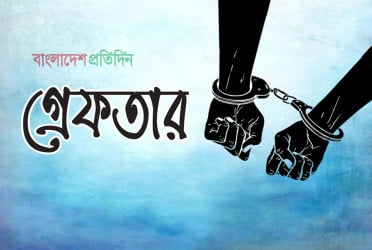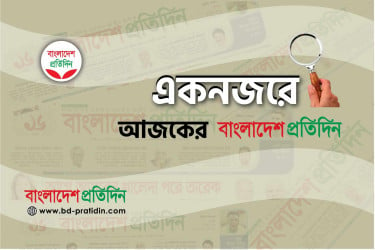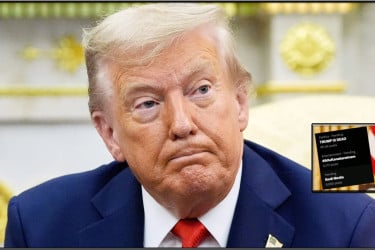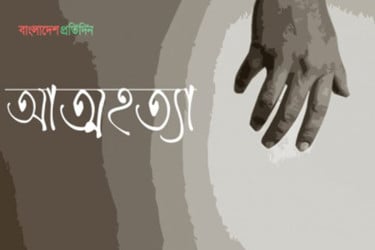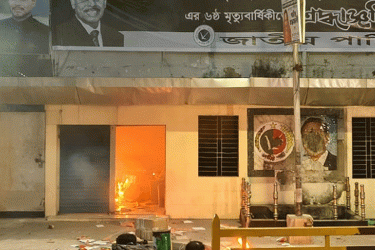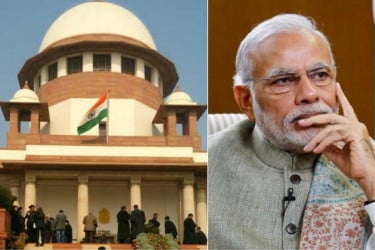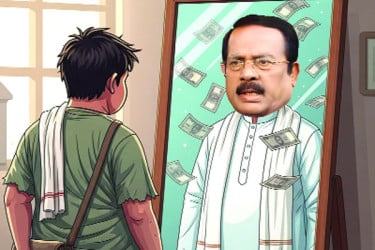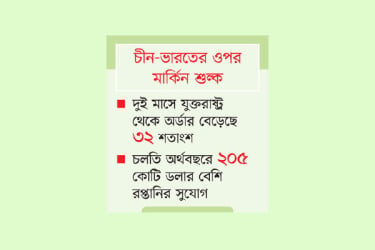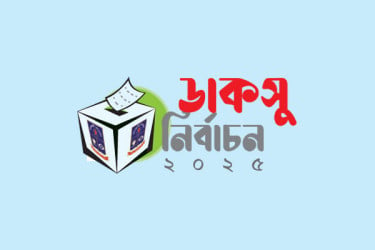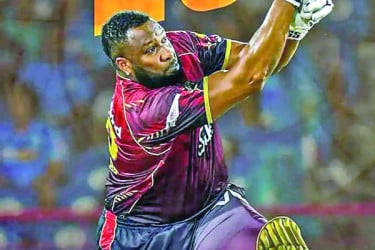গত কয়েক বছর ধরে রেকর্ড পরিমাণ ইলিশ উৎপাদন হলেও ভারতের বাজারে এ মাছের রপ্তানি উদ্বেগজনক হারে কমছে। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) সর্বশেষ তথ্যে দেখা গেছে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ভারতে ইলিশ রপ্তানির মূল্য মাত্র ৫৩ লাখ ৭০ হাজার মার্কিন ডলার, যা ২০২০-২১ অর্থবছরের ১ কোটি ৬৪ লাখ ৩০ হাজার ডলারের তুলনায় প্রায় ৬৭ শতাংশ কম। গত তিন অর্থবছর ধরেই রপ্তানির এই ধস লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে রপ্তানির পরিমাণ ছিল ১ কোটি ২২ লাখ ৭০ হাজার ডলার, যা পরের বছর সামান্য বেড়ে হয় ১ কোটি ২৮ লাখ ৩০ হাজার ডলার। ২০২৩-২৪ সালে তা নেমে আসে ৭৯ লাখ ডলারে এবং সর্বশেষে ৫৩ লাখ ৭০ হাজার ডলারে এসে ঠেকেছে। অন্যদিকে ইলিশ উৎপাদনে বাংলাদেশ অগ্রগতি অর্জন করেছে। মৎস্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৩ লাখ ৫১ হাজার টন ইলিশ উৎপাদনের বিপরীতে ২০২২-২৩ অর্থবছরে উৎপাদন দাঁড়ায় ৫ লাখ ৭১ হাজার টনে। সরকার ঘোষিত অভয়াশ্রম, প্রজনন মৌসুমে মাছ ধরা নিষিদ্ধ এবং জেলেদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রমের মাধ্যমে এই বৃদ্ধির কৃতিত্ব ধরে রাখা সম্ভব হচ্ছে।
খাতসংশ্লিষ্টরা বলছেন, উৎপাদন বাড়লেও রপ্তানিতে রয়েছে নানা প্রতিবন্ধকতা। একদিকে দেশে চাহিদা বাড়ছে অন্যদিকে রপ্তানির অনুমতির জটিলতা। এ ছাড়াও পরিবহন ও শীতলীকরণ ব্যয় বৃদ্ধির পাশাপাশি ভারতের সঙ্গে বিদ্যমান অস্থির বাণিজ্যনীতি। ইপিবির এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, ‘বিশেষ করে দুর্গাপূজার সময়ে পশ্চিমবঙ্গে ইলিশের চাহিদা খুব বেশি। কিন্তু রপ্তানি অনুমতির অনিশ্চয়তা ও দীর্ঘসূত্রতার কারণে ব্যবসায়ীরা সময়মতো প্রস্তুতি নিতে পারেন না।’ তিনি আরও বলেন, রপ্তানির জন্য কোনো বার্ষিক বা দীর্ঘমেয়াদি নীতিমালা না থাকায় ব্যবসায়ীরা বছরের অন্য সময় ইলিশ রপ্তানির বিষয়ে আগাম সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না, যার ফলে বাজার তৈরি হচ্ছে না। বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে ইলিশ দীর্ঘদিন ধরে কূটনৈতিক সম্পর্কের প্রতীক হয়ে আছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশ সাধারণত দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার মাধ্যম হিসেবে স্বল্প পরিমাণ ইলিশ রপ্তানির অনুমতি দিয়ে থাকে। কিন্তু বিশ্লেষকরা বলছেন, এ ধরনের প্রতীকী রপ্তানি স্থায়ী বাণিজ্যিক কাঠামো গঠনে সহায়ক নয়। দেশের শীর্ষ একটি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের এক কর্মকর্তা বলেন, ‘ইলিশ কূটনীতি রাজনৈতিকভাবে তাৎক্ষণিক সুফল দিতে পারে, কিন্তু এতে রপ্তানিকারকরা বছরের পর বছর ধরে টেকসই সরবরাহ চেইন তৈরি করতে পারেন না।’
বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ, সরকারের উচিত ইলিশ রপ্তানির জন্য একটি পূর্বানুমেয় ও স্থায়ী কাঠামো তৈরি করা। এতে দীর্ঘমেয়াদি রপ্তানি পরিকল্পনা, শীতল শৃঙ্খল (কোল্ড চেইন) ব্যবস্থা, নির্ভরযোগ্য বাণিজ্য চুক্তি, মজুত পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা থাকতে পারে। কারণ শুধু সংস্কৃতি নয়, অর্থনীতিতেও ইলিশের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। এটি দেশের মোট মাছ উৎপাদনের প্রায় ১২ শতাংশ এবং মোট জিডিপির ১ শতাংশের বেশি জোগান দেয়। ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরে ইলিশ উৎপাদন ছিল মাত্র ২ লাখ ১০ হাজার টন। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৫ লাখ ২০ হাজার টনে, যদিও ২০২২-২৩ অর্থবছরের ৫ লাখ ৭১ হাজার টনের তুলনায় তা ৮ দশমিক ৭৭ শতাংশ কম। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, চাঁদপুরের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোহাম্মদ আবু কাওসার দিদার বলেন, গত বছর জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত মৌসুমে খারাপ আবহাওয়ার কারণে অনেক জেলে নদী বা সমুদ্রে যাননি। ফলে প্রায় ৪০ হাজার টন কম ইলিশ ধরা পড়েছে। তিনি আরও বলেন, মা ইলিশ রক্ষায় অক্টোবর ১২ থেকে নভেম্বর ২ পর্যন্ত ২২ দিনের নিষেধাজ্ঞা দিলেও অনেকেই তা মানেননি। নিষেধাজ্ঞা অমান্য করায় প্রজনন হ্রাস পেয়েছে। এ ছাড়া পরিবেশগত বিপর্যয় ও নদীপথে পানির স্তর কমে যাওয়াও ইলিশের স্বাভাবিক চলাচলে বাধা সৃষ্টি করছে। অনেক জায়গায় ৫ মিটার গভীরতার প্রয়োজন থাকলেও নদীর গভীরতা এখন মাত্র ২-৩ মিটার, ফলে মাইগ্রেশন ব্যাহত হচ্ছে।
উৎপাদন বাড়লেও নীতিনির্ধারণী অস্থিরতা ও কূটনৈতিক প্রতীকের ফাঁদে পড়ে ইলিশ রপ্তানির সম্ভাবনা কাজে লাগাতে পারছে না বাংলাদেশ। সময় এসেছে একে পেশাগত ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব দিয়ে দেখার।