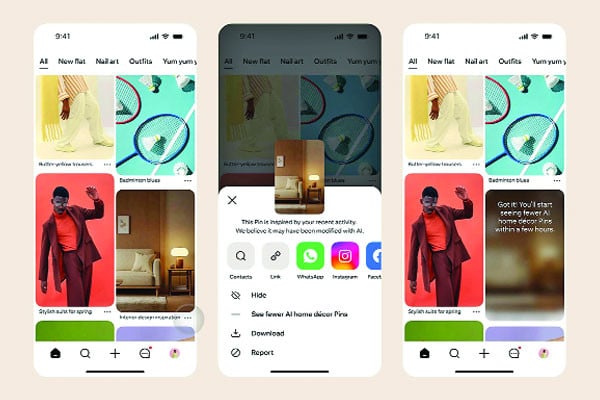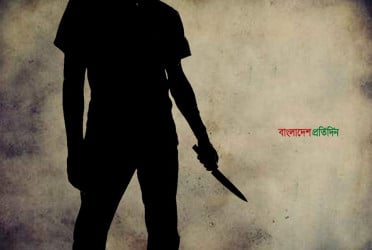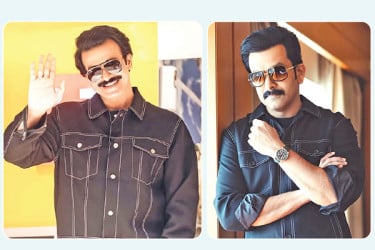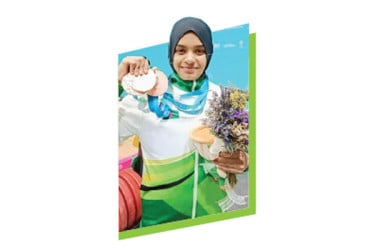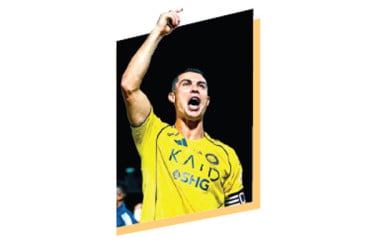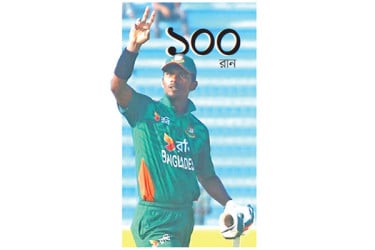মহাকাশ শক্তি
মহাকাশের কক্ষপথ থেকে সৌরশক্তি সংগ্রহ করে তা পৃথিবীতে আলোক রশ্মি আকারে পাঠানো-এই ধারণাটি কয়েক দশক পুরোনো। তবে আজ বেশ কিছু কোম্পানি দাবি করছে, তারা এটিকে অবশেষে বাস্তবে পরিণত করতে চলেছে ...
বিজ্ঞান কল্পকাহিনিতে দীর্ঘদিন ধরে আবদ্ধ থাকা একটি ধারণা এবার বাস্তবে রূপ নিতে যাচ্ছে-কক্ষপথ থেকে সৌরশক্তি সংগ্রহ করে পৃথিবীতে রশ্মি আকারে পাঠানো। এই প্রকল্প নিয়ে কাজ করছে বিশ্বজুড়ে একাধিক কোম্পানি, যারা বিশ্বাস করে মহাকাশভিত্তিক সৌরশক্তি (Space-Based Solar Power) ভবিষ্যতে পৃথিবীর পরিচ্ছন্ন শক্তির চাহিদা পূরণের প্রধান হাতিয়ার হতে পারে।
এই ধারণার প্রাথমিক পরীক্ষা শুরু হয়ে গেছে। ফ্লোরিডার জ্যাকসনভিল জাগুয়ার্স স্টেডিয়ামে স্টার ক্যাচার (Star Catcher) নামক একটি কোম্পানি সম্প্রতি এক যুগান্তকারী পরীক্ষা চালায়। মাঠের এক প্রান্ত থেকে ফ্রেসনেল লেন্সের মাধ্যমে সূর্যের আলো সংগ্রহ করে ১০০ ওয়াট শক্তি প্রায় ১০৫ মিটার দূরত্বে অবস্থিত স্ক্রিনে রশ্মি আকারে নিক্ষেপ করা হয়। স্টার ক্যাচারের প্রধান নির্বাহী অ্যান্ড্রু রাশ বলেন, ‘এটি মহাকাশে স্যাটেলাইটে শক্তি সরবরাহের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের ধাপ।’
কেন মহাকাশ শক্তি?
পৃথিবীর পৃষ্ঠে স্থাপিত সৌর প্যানেলগুলো আবহাওয়া, বায়ুমণ্ডল এবং দিন-রাতের চক্রের কারণে সীমিত। বায়ুমণ্ডল প্রায় ৩০% সৌরশক্তি প্রতিফলিত করে এবং ২৫% শোষণ করে নেয়। কিন্তু মহাকাশে এই প্যানেলগুলো প্রায় ২৪ ঘণ্টা পূর্ণ সৌর আলো সংগ্রহ করতে পারে, যেখানে শক্তির ঘনত্ব পৃথিবীতে থাকা সৌরশক্তির তুলনায় ১০ গুণেরও বেশি। ইউকে সংস্থা স্পেস সোলারের সহপ্রতিষ্ঠাতা ডেভিড হোমফ্রে যুক্তি দেন যে, মহাকাশভিত্তিক সৌরশক্তি একাই ইউরোপের নবায়নযোগ্য শক্তির চাহিদার ৮০% পর্যন্ত সরবরাহ করতে পারে, যা জীবাশ্ম জ্বালানির বিকল্প হিসেবে গ্রিন এনার্জির চাহিদা মেটাতে গুরুত্বপূর্ণ। সামরিক বাহিনী থেকে দুর্যোগ-পরবর্তী বিদ্যুতের প্রয়োজন হওয়া গ্রামীণ সম্প্রদায়-সবার জন্য এটি শক্তি সরবরাহের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে পারে।

এই প্রযুক্তি যেভাবে কাজ করে
মহাকাশভিত্তিক সৌর প্যানেলগুলো সূর্যালোককে বিদ্যুতে রূপান্তর করে, যা বায়ুমণ্ডলের ওপরে থাকার কারণে আরও কার্যকর হয়। একবার সংগ্রহ করা হলে এই শক্তি মাইক্রোওয়েভ বা লেজার রশ্মি হিসেবে পৃথিবীতে পাঠানো হয়। স্থলভাগে অবস্থিত বিশাল গ্রাউন্ড অ্যান্টেনা (রিসিভিং স্টেশন) সেই রশ্মিকে আবার ব্যবহারযোগ্য বিদ্যুতে রূপান্তরিত করে। তবে অর্থনৈতিকভাবে সফল হওয়ার জন্য প্রতিটি স্যাটেলাইটকে গিগাওয়াট স্কেলে শক্তি উৎপাদন করতে হবে, যার জন্য কক্ষপথে বিশাল কাঠামো একত্রিত করার প্রয়োজন। এই ধারণাটি প্রথম ১৯৪১ সালে বিজ্ঞান-কল্পকাহিনি লেখক আইজ্যাক আসিমভ তাঁর ‘রিজন’ গল্পে তুলে ধরেছিলেন। ১৯৭০-এর দশকে নাসা এই ধারণা নিয়ে গবেষণা করলেও প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিক বাধা ছিল। কিন্তু ১৯৯০-এর দশকে নাসার সাবেক পদার্থবিদ জন ম্যানকিন্সের গবেষণায় দেখা যায় যে, সৌর কোষ ও অন্যান্য প্রযুক্তির অগ্রগতির কারণে এই ধারণাটি আরও কার্যকর হতে যাচ্ছে।
বর্তমান অগ্রগতি এবং বৈশ্বিক উদ্যোগ
গত এক দশকে মহাকাশে বস্তু উৎক্ষেপণের খরচ কমা, স্পেসএক্সের স্টারশিপের মতো বিশাল রকেট ও রোবোটিক্স প্রযুক্তির উন্নতির ফলে SBSP-তে আন্তর্জাতিক আগ্রহ বেড়েছে। ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও চীনসহ একাধিক দেশ এতে বিনিয়োগ করছে।
► যুক্তরাজ্য : সরকার এই খাতে ৪.৩ মিলিয়ন পাউন্ড তহবিল দিয়েছে। স্পেস সোলার ২০৫০ সালের মধ্যে বিশ্বের মোট শক্তির ২০% সরবরাহ করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে। তারা ‘ক্যাসিওপিয়া’ নামক কাঠামো (১.৮ কিমি. প্রশস্ত) ভূস্থির কক্ষপথে তৈরির পরিকল্পনা করছে, যা হিথ্রো বিমানবন্দরের আকারের স্টেশনে রেডিও তরঙ্গ শক্তি পাঠাবে।
► চীন : বিজ্ঞানীরা ওমেগা ২.০ নামে একটি প্রোটোটাইপ মহাকাশ সৌরশক্তি স্যাটেলাইট নিয়ে কাজ করছে। পরীক্ষায় মাইক্রোওয়েভের মাধ্যমে তারা ৫৫ মিটার দূরত্বে ২,০৮১ ওয়াট শক্তি প্রেরণ করতে সক্ষম হয়েছেন।
► মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র : ইথারফ্লাক্স উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন ইনফ্রারেড লেজার ব্যবহার করে পৃথিবীর কক্ষপথে স্যাটেলাইটের বহর স্থাপন করতে চায়। নিরাপত্তা নিশ্চিতের জন্য এটি এমনভাবে ডিজাইন করা হচ্ছে যাতে কোনো কিছু পথে এলে তা তাৎক্ষণিকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। ২০২৬ সালে ১ কিলোওয়াট লেজার পৃথিবীতে পাঠানোর জন্য তারা একটি প্রদর্শন স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের পরিকল্পনা করেছে। অন্যদিকে ২০২৭ সালে ভার্টাস সলিস ২ লাখ স্যাটেলাইট নিয়ে একটি নক্ষত্রপুঞ্জ চালু করার পরিকল্পনা করেছে, যা বিদ্যুতের খরচ নাটকীয়ভাবে কমিয়ে প্রতি মেগাওয়াট ঘণ্টায় মার্কিন ডলারে মাত্র ০.৫০-এ নামিয়ে আনার স্বপ্ন দেখছে।
এই প্রযুক্তির চ্যালেঞ্জ ও জটিলতা
মহাকাশে এত বড় পরিসরে বিপুল সংখ্যক স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ ও পরিচালনা করা এক বিশাল চ্যালেঞ্জ। ইউরোপীয় স্পেস এজেন্সির ফ্রান্সেস্কা লেটিজিয়া সতর্ক করে বলেছেন, ‘কক্ষপথে সংঘর্ষ এড়ানো একটি বড় সমস্যা, এবং সামান্য দুর্ঘটনাও এই উদীয়মান শিল্পকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।’ এ ছাড়াও মিসিসিপি বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাকাশ আইনজীবী মিশেল হ্যানলন বলেন, ১৯৬৭ সালের আউটার স্পেস ট্রিটি অনুসারে কোনো দেশ কক্ষপথের মালিকানা দাবি করতে পারবে না। তাই যখন এক বর্গমাইল নিয়ে কথা, তখন আইনগত জটিলতাও বাড়তে পারে।
তথ্যসূত্র : বিবিসি