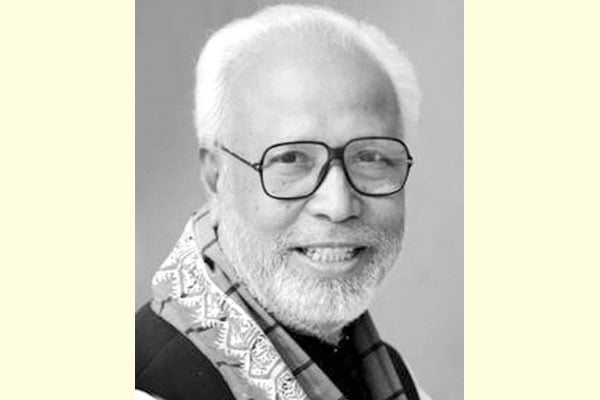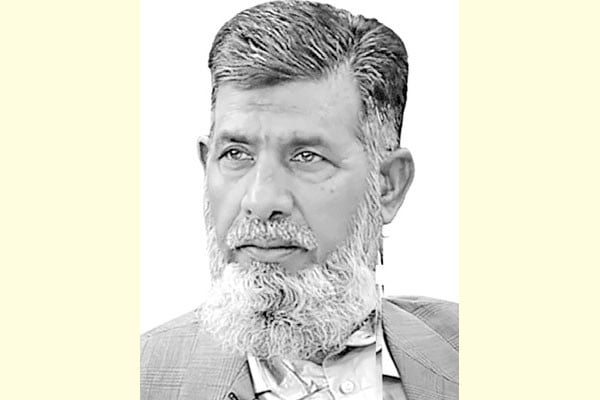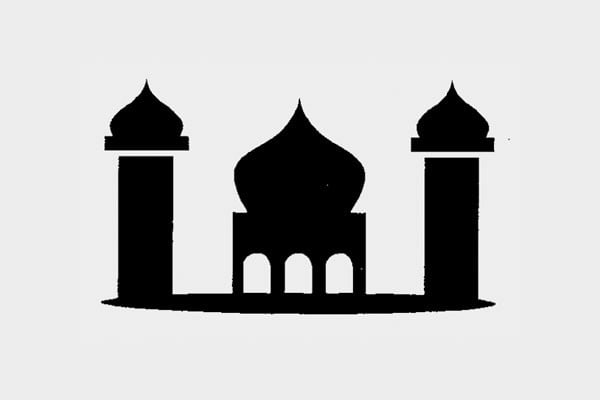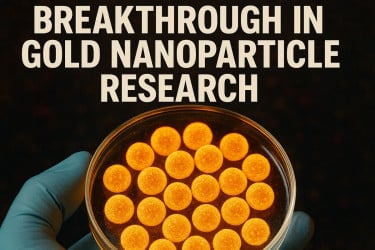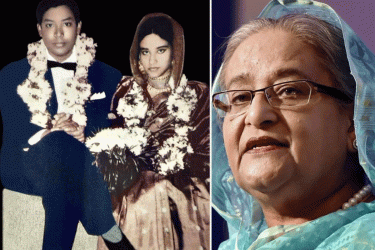কোরবানির ঈদ মোটামুটি নির্বিঘ্নে কেটেছে। মানুষজনের রাস্তাঘাটে কিছুটা কষ্ট হলেও তা অনেকটা সহনীয় পর্যায়ে ছিল। আমরা বেশ কয়েক মাস নির্বাচনে জড়িয়ে আছি। ২১ জুন বাসাইলের পৌর নির্বাচন। সেখানে মূলত তিনজন মেয়র প্রার্থী। একজন আওয়ামী লীগ, একজন বিএনপি, অন্যজন কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের। বলতে গেলে নির্বাচন অনেকটাই আনন্দঘন পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে। নৌকার প্রার্থী ছিলেন আবদুর রহিম। অনেক বছর দেশের বাইরে ছিলেন। কিছু টাকাপয়সা উপার্জন করেছেন। তা ছাড়া গত পাঁচ বছর বাসাইলের মেয়র ছিলেন। স্বাধীনতার পরপরই জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল নামে একটি দলের জন্ম হয়েছিল। তারা তখন বুঝতে পেরেছিলেন কি না জানি না। তবে আমি জাসদকে স্বাধীনতার সন্তান হিসেবেই আগাগোড়া মনে করেছি। দেশ হলে দেশে অনেক রাজনৈতিক দল হবে। আর সেখানে জাসদ ছিল বাংলাদেশের প্রথম রাজনৈতিক দল। তারা যদি সঠিক পথে থাকতে পারত তাহলে তাদের আজকের অবস্থা হতো না। জাসদ গঠন করার পর যেখানেই সভা-সমাবেশ করেছে সেখানেই প্রচুর লোক হয়েছে। টাকাপয়সায়ও তাদের তেমন কোনো অসুবিধা হয়নি। কারণ মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত শত্রুরা কোথাও দাঁড়াবার জায়গা না পেয়ে জাসদের আশ্রয়ে নিজেদের আড়াল করার চেষ্টা করেছে। যে কারণে তাদের যে কোনো অনুষ্ঠানে আশাতীত লোক হয়েছে। তা ছাড়া সত্যিকার অর্থে মেধাবী যুবসমাজ, ছাত্রছাত্রী অধিকাংশই জাসদের পতাকাতলে স্থান নিয়েছিল। তাই তারা তাদের প্রতি সমর্থন দেখে কিছুটা উৎসাহী না হয়ে পারেনি। তারা যথার্থই উৎসাহী হয়েছে। কিন্তু দিন যতই যাচ্ছিল ততই তাদের দলে ভাটির টান শুরু হয়েছিল। এরপর হঠাৎ বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে এক মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি করা হয়। অল্প সময়ের মধ্যেই খন্দকার মোশতাক, তারপর এক বিচারপতি রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হন। তারপর হ্যাঁ-না ভোটের মাধ্যমে জিয়াউর রহমান আসেন ক্ষমতায়। মুক্তিযুদ্ধ করেছেন অনেকেই। কিন্তু সেনাবাহিনীর মধ্যে মুক্তিযুদ্ধে জিয়াউর রহমান সবচেয়ে বেশি প্রচার পেয়েছেন। সামরিক বাহিনী থেকে ক্ষমতায় এসে মুক্তিযুদ্ধের ভূমিকা তুলে ধরে জিয়াউর রহমান অনেকটাই এগিয়ে যান। যেটা জাসদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। দ্বিতীয়ত, জাসদ শুধু রাজনৈতিক দল ছিল না। তারা একটা ক্যাডারভিত্তিক দল গঠনেরও চেষ্টা করেছিল। জাসদের সভাপতি ছিলেন মেজর এম এ জলিল, সাধারণ সম্পাদক আ স ম আবদুর রব। অন্যদিকে জাসদের ক্যাডার গণবাহিনী যার প্রধান ছিলেন কর্নেল তাহের বীরউত্তম ও হাসানুল হক ইনু। জাসদের গণবাহিনী অনেক লোককে হত্যা করে। টাঙ্গাইলে যে কজন মুক্তিযোদ্ধা ও আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী নিহত হয়েছেন তার ৯০ ভাগ জাসদের গণবাহিনী করেছে। বাসাইলে প্রতিদ্বন্দ্বী আবদুর রহিম ছিলেন গণবাহিনীর সদস্য। কিন্তু কয়েক যুগ পর সেই গণবাহিনীর নেতা-কর্মী হিসেবে আবদুর রহিমের আওয়ামী লীগ থেকে মনোনয়ন পেতে কোনো অসুবিধা হয়নি। যদিও এবার নির্বাচনে আবদুর রহিম এবং বিএনপির এনায়েত করীম অটল, গামছার দল কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের কাছে পরাজিত হয়েছেন। বলতেই হবে যে বাসাইলের নির্বাচন সরকারি প্রভাবমুক্ত স্বতঃস্ফূর্ত হয়েছে। আবার ১৭ জুলাই সখিপুর ও কালিহাতীতে বেশ কয়েকটি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন হচ্ছে। আমার বিশ্বাস, এ কটি নির্বাচন সরকারি প্রভাবমুক্ত হবে। সেদিনও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা এবং কথা হয়েছে। সরকার এসব নির্বাচনে কোনো প্রভাব খাটাবে না। নির্বাচন কমিশন চায় অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন হোক। এখন অবধি আমার বিশ্বাস, সরকার এবং নির্বাচন কমিশন ভবিষ্যতের চিন্তায় তাদের কথা রাখবে। সরকারি দলের নেতানেত্রীদের অসুবিধা তাদের পদবি নিয়ে তারা নির্বাচনী এলাকায় যেতে পারছেন না। এদিকে  বর্তমানে কোনো পদপদবি না থাকায় দলের প্রধান হিসেবে ছোটাছুটি করায় আমার কোনো অসুবিধা নেই। তাই ছোটাছুটি করছি। কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের দুজন নেতা স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছে। তাই তাদের দল থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। দেখা যাক, হতেয়াতে হুমায়ুন, বড়চওনায় লাল মিয়া কতটা কী করে। এখানে আমার দেখার একমাত্র বিষয় হচ্ছে নির্বাচনটা অবাধ, উৎসবমুখর হোক। যে কোনো ভোটার যাতে নির্বিবাদে কেন্দ্রে গিয়ে অবাধে ভোট দিতে পারে। আমার মনে হয় কালিহাতী আর সখিপুরে যে কটি চেয়ারম্যান নির্বাচন হচ্ছে সবকটি ভালো হবে, প্রভাবমুক্ত হবে এটাই আমার বিশ্বাস। বেশ কিছুদিন অনেকেরই মনে হয়েছিল ২০-৫০ লাখ টাকা খরচ করে নৌকা পেলে তার আর কিছু করতে হবে না। নৌকা পেলেই পাস। সেটা এবার হবে না। যথাযথ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছ নির্বাচন করাতে না পারলে নির্বাচন কমিশন যেমন প্রশ্নের সম্মুখীন হবে, তেমনি সরকারও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই সুন্দর প্রভাবমুক্ত নির্বাচন করে সরকার এবং নির্বাচন কমিশন কিছুটা সম্মান বা আস্থা অর্জনের চেষ্টা করতে পারে। সত্যিকার অর্থেই নির্বাচন পদ্ধতি সম্পর্কে মানুষের মধ্যে এক মারাত্মক বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছে। এ মনোভাব নির্বাচন কমিশন অতিক্রম করতে না পারলে ভবিষ্যতে এক ভয়াবহ আকার ধারণ করবে।
বর্তমানে কোনো পদপদবি না থাকায় দলের প্রধান হিসেবে ছোটাছুটি করায় আমার কোনো অসুবিধা নেই। তাই ছোটাছুটি করছি। কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের দুজন নেতা স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছে। তাই তাদের দল থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। দেখা যাক, হতেয়াতে হুমায়ুন, বড়চওনায় লাল মিয়া কতটা কী করে। এখানে আমার দেখার একমাত্র বিষয় হচ্ছে নির্বাচনটা অবাধ, উৎসবমুখর হোক। যে কোনো ভোটার যাতে নির্বিবাদে কেন্দ্রে গিয়ে অবাধে ভোট দিতে পারে। আমার মনে হয় কালিহাতী আর সখিপুরে যে কটি চেয়ারম্যান নির্বাচন হচ্ছে সবকটি ভালো হবে, প্রভাবমুক্ত হবে এটাই আমার বিশ্বাস। বেশ কিছুদিন অনেকেরই মনে হয়েছিল ২০-৫০ লাখ টাকা খরচ করে নৌকা পেলে তার আর কিছু করতে হবে না। নৌকা পেলেই পাস। সেটা এবার হবে না। যথাযথ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছ নির্বাচন করাতে না পারলে নির্বাচন কমিশন যেমন প্রশ্নের সম্মুখীন হবে, তেমনি সরকারও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই সুন্দর প্রভাবমুক্ত নির্বাচন করে সরকার এবং নির্বাচন কমিশন কিছুটা সম্মান বা আস্থা অর্জনের চেষ্টা করতে পারে। সত্যিকার অর্থেই নির্বাচন পদ্ধতি সম্পর্কে মানুষের মধ্যে এক মারাত্মক বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছে। এ মনোভাব নির্বাচন কমিশন অতিক্রম করতে না পারলে ভবিষ্যতে এক ভয়াবহ আকার ধারণ করবে।
তা ছাড়া সার্বিক অর্থে দেশের অবস্থা খুব একটা ভালো না। বাজারের দিকে চোখ পড়লেই মানুষের হতাশা বোঝা যায়। কাঁচা মরিচের দাম হাজার টাকা! এটা কেউ কোনো দিন কল্পনাও করেনি। ভারত থেকে কয়েক টন কাঁচা মরিচ এসেছে। তাতেও খোলা বাজারে কাঁচা মরিচের দাম তিন শ-চার শর নিচে নামেনি। কোনো কোনো জায়গায় এর থেকেও বেশিতে বেচাকেনা হচ্ছে। তা ছাড়া আলু-পিঁয়াজ-রসুন-আদা কোনো কিছুর দাম নিয়ন্ত্রণে নেই। মাছ, মাংস, তরিতরকারি এ যেন সব সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে। বাজারদর অল্প কদিনেই দ্বিগুণ-তিন গুণ হয়ে গেলেও সাধারণ মানুষের উপার্জন বাড়েনি। বিশেষ করে বেসরকারি চাকরিজীবীদের জন্য এ এক মরণফাঁদ। এ ফাঁদ থেকে কবে যে সাধারণ মানুষ পরিত্রাণ পাবে কেউ জানে না। এ ছাড়া ঘুষ ছাড়া কোনো নতুন চাকরিবাকরি নেই। বেসরকারি খাতেও যা দু-চারটা চাকরিবাকরি ঘুষ ছাড়া হতো, সেখানেও কেমন যেন একটা স্থবির অবস্থা। কোনোখানেই কোনো স্বতঃস্ফূর্ততা নেই। আর রাজনৈতিক দলাদলি, মারামারি লেগেই আছে। সাধারণ মানুষ ভাবছে সরকার প্রায় সবকিছু মুক্তিযোদ্ধাদের দিয়ে দিয়েছে বা দিচ্ছে। ঢাকা সিটির যারা ময়লা পরিষ্কার করে তারা অবসরে গেলে তাদেরও অবসর ভাতা হয় ৪০-৫০ হাজার টাকা। মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে প্রথম শুরু করা হয়েছিল যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ভাতা ৭৫ টাকা দিয়ে। সেটা এখন ২৫-৩০ হাজারে উন্নীত হয়েছে। স্বাধীনতার পরপরই একমাত্র যুদ্ধাহতদের ভাতা প্রদানের একটা বিধান ছিল। অনেক পরে এই সেদিন সাধারণ মুক্তিযোদ্ধাদের ২০ হাজার করে ভাতা দেওয়া হচ্ছে। এ ভাতা প্রদানেও কত শুভংকরের ফাঁক চিন্তা করে শেষ করা যায় না। আগে ছিল শুধু যুদ্ধাহত ভাতা। বর্তমান সরকার যুদ্ধাহত ভাতা বৃদ্ধি করে সাধারণ মুক্তিযোদ্ধাদেরও ভাতা দিচ্ছে। এ ছাড়া মুক্তিযুদ্ধে অপরিসীম ভূমিকা রাখার জন্য খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদেরও ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বর্তমান সরকার সাধারণ মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা দেয়, যুদ্ধাহতদের ভাতা দেয় এবং যারা খেতাব পেয়েছেন তাদের ভাতার প্রচলন করেছে। অনেক মুক্তিযোদ্ধাই এ তিনটি ভাতা বেশ কিছুদিন একসঙ্গেই পেয়েছেন। কোনো এক রাজাকারের ছেলে মুক্তিযুদ্ধ-বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের একসময় সচিব হওয়ায় তিনি এক নোট দিয়ে গেছেন, মুক্তিযোদ্ধা, যুদ্ধাহত এবং খেতাবপ্রাপ্ত এ তিনটি ভাতার যেটি সবচাইতে বেশি শুধু তিনি সেই একটি ভাতাই পাবেন। যে কারণে অনেকেই মুক্তিযোদ্ধা ভাতা পাচ্ছেন না, খেতাবপ্রাপ্তের পাচ্ছেন না, শুধু যুদ্ধাহত হিসেবে ভাতা পাচ্ছেন। কারণ যুদ্ধাহত ভাতা একটু বেশি। আসলেই সবকিছুতেই কেমন যেন গা ছাড়া ভাব। কেউ তেমন কিছু তলিয়ে দেখেন না। যা কিছু করেন গা বাঁচাবার জন্য করেন। অথচ মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে কত কথা, কত কাহিনি। সাধারণ মানুষ মনে করে মুক্তিযোদ্ধাদের সবকিছু দিয়ে দেওয়া হয়েছে বা হচ্ছে। শত শত মুক্তিযোদ্ধা আমার কাছে আসে। তাদের কত সমস্যা। অনেকেই তালিকাভুক্তিই হয়নি। যখন জিজ্ঞেস করি, স্বাধীনতার ৫৩ বছরেও কেন তার নাম তালিকাভুক্ত হয়নি। তাদের সহজ সরল উত্তর, বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নির্মমভাবে নিহত হলে শুধু মুক্তিযোদ্ধাদের ধরে ধরে জেলে পাঠানো হয়েছে। আপনি বঙ্গবন্ধুর হত্যার প্রতিবাদ-প্রতিরোধ গড়ে তুললে মুক্তিযোদ্ধা তো দূরের কথা কাদেরিয়া বাহিনীতে ছিলেন শুনলেই বিনা কারণে কারাগারে নিক্ষেপ। তখন আর আমার কিছু বলার থাকে না। ঘটনা ষোলো আনা সত্য। শুধু মুক্তিযোদ্ধা নয়, কাদেরিয়া বাহিনীর যোদ্ধা শোনামাত্রই ফাঁসি না হলেও তাদের জেল-জরিমানা। এক কঠিন গণ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ১৯৯০ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসে কলকাতা থেকে ঢাকা ফিরেছিলাম। আমার ফেরা নিয়ে অনেক তেলেসমাতি হয়েছে। পাসপোর্ট, ভিসা কোথায়? আমার কাছে কোনো পাসপোর্ট ছিল না। সারা পৃথিবীতে দেশত্যাগীদের আন্তর্জাতিক নিয়মে রিফিউজি আইডেন্টিটি দেওয়া হয়। বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বোন শেখ হাসিনার অনেক দেনদরবারে আমি আন্তর্জাতিক রিফিউজি কার্ড পেয়েছিলাম। তাই নিয়ে ১৯৮৯-’৯০ সালে দুবার ইংল্যান্ডে গিয়েছিলাম। তারপর দেশে ফিরি। আমার কাছে সে আইডেন্টিটি কার্ডও ছিল না। আইডেন্টিটি কার্ড ছিল আমার ব্যক্তিগত সহকারী ফরিদ আহমেদের কাছে। ইমিগ্রেশনের লোকজন আমার পাসপোর্টের কথা জিজ্ঞেস করলে সে সরল বিশ্বাসে সেই আইডেন্টিটি কার্ড দেখায়। সেখানে এক মাসের সময় দিয়ে সিল-ছাপ্পর মেরে ছেড়ে দেয়। যেহেতু আমি বিমানবন্দর থেকে সরাসরি বেরিয়ে এসেছিলাম, সেহেতু আমাকে নিয়ে বিমানবন্দরে কোনো আনুষ্ঠানিকতা সেদিন হয়নি। পরে ১৭ জানুয়ারি আমাকে জেলখানায় নিলে ধীরে ধীরে এসব জানতে পারি। ১৭ জানুয়ারি ’৯১ থেকে ১৮ আগস্ট ’৯১ পর্যন্ত জেল খেটে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের আদেশে মুক্তি পেয়ে বেরিয়ে আসি। মুক্তির সময় আমি ছিলাম বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রিজন সেলে। ১৬ ডিসেম্বর ঢাকায় ফিরে যেমন কোনো আওয়ামী লীগ নেতাকে পাইনি, তেমনি প্রিজন সেল থেকে বেরিয়ে কোনো আওয়ামী নেতাকে দেখতে পাইনি। ১৬ ডিসেম্বর ’৯০ ঢাকা বিমানবন্দরে আওয়ামী লীগের বয়স্ক নেতা হিসেবে শুধু পেয়েছিলাম আওয়ামী লীগের যুগ্মসম্পাদক টাঙ্গাইলের কৃতী সন্তান শামসুর রহমান খান শাজাহানকে, অন্যদিকে বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু গোপালগঞ্জের শামসুদ্দিন আহমেদ। আমি ’৭৫-এ তাঁর সঙ্গে জেলা গভর্নর ছিলাম। ছাত্রদের মধ্যে হাবিব এবং অসীম কুমার উকিল, অন্যদিকে আমার বড় ভাই লতিফ সিদ্দিকী বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন। বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরোবার পর একমাত্র যুবলীগের সভাপতি জনাব মোস্তফা মহসীন মন্টুকে পেয়েছিলাম। তিনি বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ধানমন্ডি ৩২-এর বাড়ি হয়ে ২০/৩০ বাবর রোড পর্যন্ত এসেছিলেন। কেন যেন সারা জীবনই আমাদের উল্টো স্রোতে চলতে হয়েছে। বড় ভাই লতিফ সিদ্দিকী যেমন ’৬০-’৬২ সাল থেকে সারা দেশকে মাতিয়ে তুলেছিলেন। কিন্তু দলীয় কোনো পদপদবি পাননি। খুব সম্ভবত ’৬০ বা ’৬২ সালে টাঙ্গাইল মহকুমাকে জেলার স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ওর আগে টাঙ্গাইল ছাত্রলীগ মহকুমা শাখা হিসেবে বৃহত্তর ময়মনসিংহের নিয়ন্ত্রণে ছিল। যদিও এখন ত্রিশাল-ভালুকা-শ্রীপুর-জয়দেবপুর হয়ে ময়মনসিংহ থেকে সরাসরি ঢাকা যাওয়া যায়। কিন্তু ’৬০-’৬২ সালে তেমন ছিল না। গাড়িপথে ময়মনসিংহ থেকে টাঙ্গাইল হয়ে ঢাকা যেতে হতো। তাই ময়মনসিংহের চাইতে ঢাকাই ছিল আমাদের কাছে অনেক অনেক সুবিধা। সেই সম্মেলনে বড় ভাই লতিফ সিদ্দিকী টাঙ্গাইল জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক হয়েছিলেন। তখন জনাব শাজাহান সিরাজের কোনো নামগন্ধ ছিল না। পাকিস্তানের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের টাঙ্গাইল জেলা শাখার সর্বশেষ সাধারণ সম্পাদক ছিলাম আমি। তা-ও খন্ডিত ছাত্রলীগের। আমাদের পক্ষে শতকরা ৮০ জন নেতা-কর্মী থাকার পরও স্বাধীনতার আগ পর্যন্ত আমাদের কমিটিকে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ স্বীকৃতি দেয়নি। আমাদের দিকে সভাপতি ছিলেন আবু মোহাম্মদ এনায়েত করীম আর শাজাহান সিরাজের পক্ষে সভাপতি ছিলেন আলমগীর খান মেনু ও সাধারণ সম্পাদক খন্দকার আবদুল বাতেন। মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত তারা আমাদের কোনোমতেই স্বীকার করেননি। প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রলীগ কোনোখানে সভা-সমাবেশ করলে তাদের ২০০ লোকও হতো না, আমাদের লোকসমাগম হতো ২ হাজার। কিন্তু জনাব শাজাহান সিরাজ থাকার কারণে টাঙ্গাইলের সেই দুর্বল কমিটি সব সময়ের জন্য কেন্দ্রের সহযোগিতা পেত। অল্প বয়সে বুঝতে পারতাম না, কেন এমন বিরোধিতা। কিন্তু যত দিন গড়াতে থাকে সবকিছু স্পষ্ট হয়ে যায়। ব্যক্তিস্বার্থে অন্ধ অনেক নেতার কাছে সংগঠন করতে গিয়ে ন্যায়-অন্যায়ের কোনো পার্থক্য দেখিনি। যে কারণে দলের মধ্যে উপদল হয়। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধুকে বিতর্কিত করতে, তাঁর অবদান মুছে ফেলতে বিশেষ করে টাঙ্গাইলে যারা সবচাইতে উল্লেখযোগ্য ছিলেন তারাই এখন মূল আওয়ামী লীগ। দু-চার-পাঁচ বছর আগে যারা ভাঙা কাপে চা খেতেন, যারা চায়ের দাম দিতে পারতেন না তারা অনেকেই আজ শত শত কোটি টাকার মালিক! সেখানে স্বাধীনতাবিরোধী লোকজনেরও খুব একটা অভাব নেই। তাই জীবনের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত কেন যেন আমরা স্রোতের বিপরীতে পড়ে আছি। এর শেষ কোথায় কেউ জানি না। তবে বর্তমানে আওয়ামী লীগের কোনো শত্রুর প্রয়োজন নেই। আওয়ামী লীগের লোকেরাই আওয়ামী লীগের শত্রু। আমার হয়েছে মারাত্মক বিপদ। এ পর্যন্ত হাজারের ওপর প্রস্তাব এসেছে বোন হাসিনার সঙ্গে একটু দেখা করিয়ে দিতে। সেখানে অনেক বড় বড় নেতাও আছে, সাধারণ নেতা-কর্মী তো আছেই। আর মুক্তিযোদ্ধা ও ’৭৫-এর প্রতিরোধ যোদ্ধাদের নিয়ে আরও বিপদ। রাতদিন ফোন আসে এখনো আমি সার্টিফিকেট পাইনি। ’৭৫-এর প্রতিরোধ যোদ্ধারা আসে, আমরা তো এখনো দুষ্কৃতকারী। কোনো সরকারি স্বীকৃতি নেই। ব্যাপারগুলো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়েছি। তিনি অনেকটা আন্তরিকতা নিয়েই এসব সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছেন। কিন্তু তেমন কোনো সমাধান হচ্ছে না। এটা আমার জন্য মারাত্মক মর্মযাতনার কারণ।
লেখক : রাজনীতিক
www.ksjleague.com