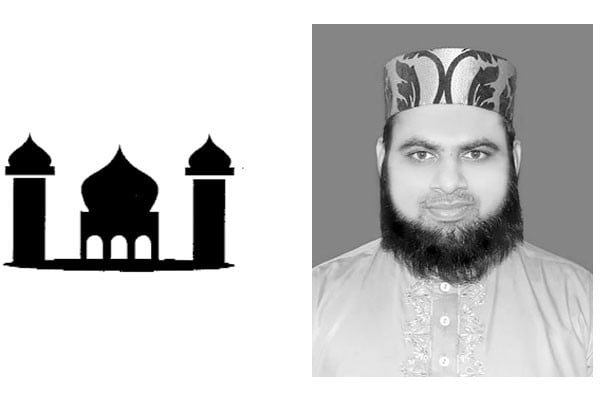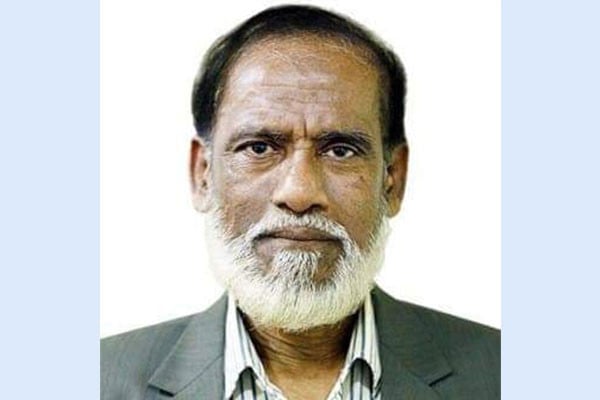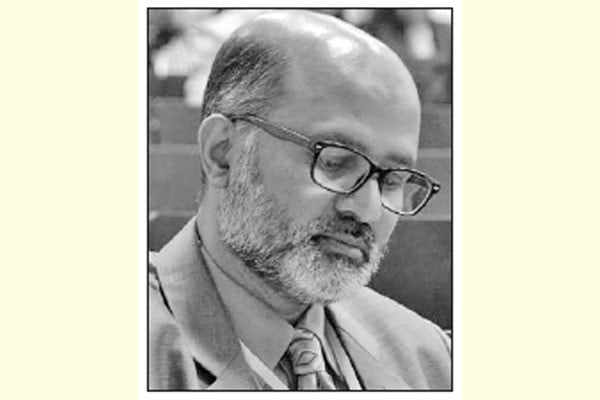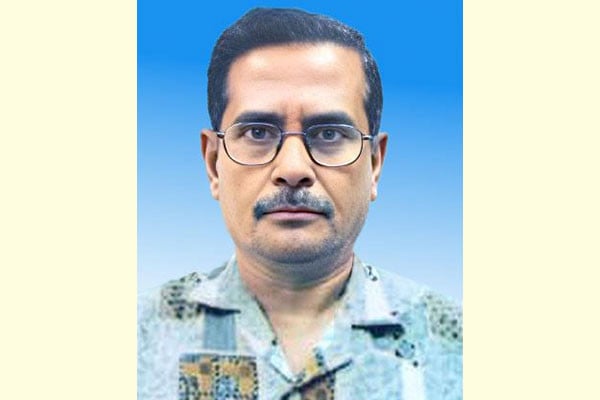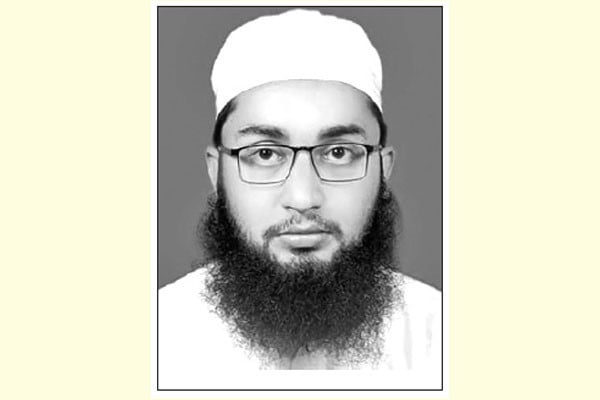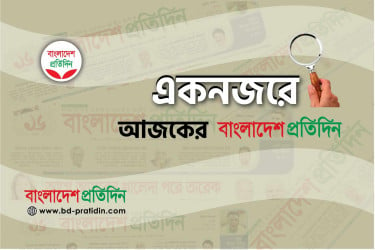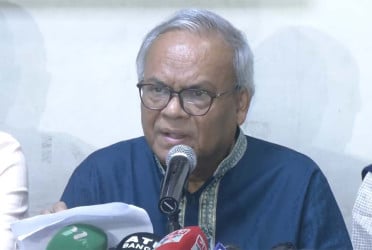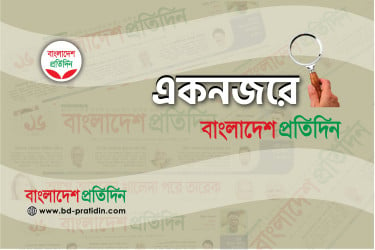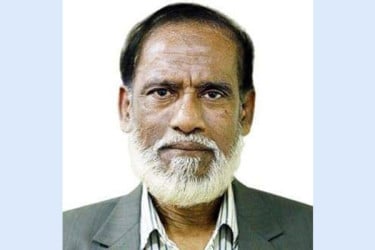চলতি বছর পদার্থবিজ্ঞানের নোবেল পুরস্কার যৌথভাবে পেয়েছেন জন ক্লার্ক, মিশেল ডেভরেট এবং জন মার্টিনিস। ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ার এই তিন গবেষক ম্যাক্রোস্কোপিক কোয়ান্টাম মেকানিক্যাল টানেলিং ও ইলেকট্রিক সার্কিটে শক্তি পরিমাপের ওপর তাদের গবেষণার জন্য। কোয়ান্টামতত্ত্ব হলো পদার্থবিদ্যার এমন একটি শাখা, যা পরমাণু ও অতি পারমাণবিক কণার আচরণ ব্যাখ্যা করে, যেখানে শক্তি ও পদার্থের সর্বনিম্ন একককে ‘কোয়ান্টা’ বা প্যাকেট হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ১৯০০ সালে এই তত্ত্বের ধারণা দেন এবং এটি কোয়ান্টাম মেকানিক্স বা কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যা নামে পরিচিত। কোয়ান্টামতত্ত্বের মূল ধারণাগুলো হলো ১. শক্তি ‘কোয়ান্টা’য় বিদ্যমান- ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের প্রস্তাবনা অনুযায়ী, শক্তি অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত না হয়ে বিচ্ছিন্ন শক্তি প্যাকেটের (কোয়ান্টা) আকারে নির্গত বা শোষিত হয়।
২. আলোর কণা-তরঙ্গ দ্বৈততা-আলোর কণা এবং তরঙ্গ-উভয় ধর্মই রয়েছে। আলোর এই ক্ষুদ্রতম শক্তি প্যাকেটকে ফোটন বলা হয়। ৩. কোয়ান্টাম মেকানিক্স-পরমাণু এবং অতি পারমাণবিক কণা স্তরে পদার্থ ও শক্তির আচরণ ব্যাখ্যা করার জন্য এই তত্ত্ব ব্যবহৃত হয় ইত্যাদি। এই আবিষ্কারের মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা কোয়ান্টাম মেকানিক্সের জটিল ঘটনাগুলো বড় পরিসরে পর্যবেক্ষণ করতে সক্ষম হয়েছেন, যা কোয়ান্টাম বলবিদ্যার অসামান্য জগতে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে। তাদের এই আবিষ্কার নতুন প্রযুক্তির এক অপার সম্ভাবনা, যা আমাদের চারপাশ থেকে তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, বোঝা ও ব্যবহার করার পদ্ধতিকে আমূল পরিবর্তন করতে সক্ষম হবে।
ম্যাক্রোস্কোপিক কোয়ান্টাম হলো ম্যাক্রোস্কোপিক বৈশিষ্ট্য যেমন যান্ত্রিক গতি, তাপ পরিবাহিতা, বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা এবং সান্দ্রতা, যা শুধু ক্লাসিক্যাল মেকানিক্সের পরিবর্তে কোয়ান্টাম মেকানিক্স দ্বারা বর্ণনা করা যায়। তাদের গবেষণার মৌলিক উপাদান ছিল ‘জোসেফসন জংশন’ নামের একটি যন্ত্র, যেখানে দুটি সুপারকন্ডাক্টরকে খুবই পাতলা একটি ইনসুলেটর দিয়ে আলাদা করা হয়েছে এবং সার্কিটে একই সঙ্গে ম্যাক্রোস্কোপিক কোয়ান্টাম টানেলিং ও বিচ্ছিন্ন শক্তিস্তর উভয়ই পর্যবেক্ষণ করতে সক্ষম হন। তারা দেখলেন, কারেন্টটি যদি খুব ছোট হয় তখন, তবে ইলেকট্রন জোড়াগুলোর প্রবাহ আটকে যায় এবং সার্কিট কোনো ভোল্টেজ তৈরি করে না। ক্লাসিক্যাল পদার্থবিজ্ঞানে এই অবস্থা স্থায়ী থাকত, প্রবাহ কখনো পুনরায় শুরু হতো না। কিন্তু কোয়ান্টাম জগতে সেই ইলেকট্রন জোড়ারগুলোর সামান্য সম্ভাবনা থাকে হঠাৎ করে ‘টানেল’ করে সেই বাধা পার হয়ে অন্য পাশে গিয়ে মুক্তভাবে প্রবাহিত হওয়ার। যার ফলে পরিমাপযোগ্য ভোল্টেজ সৃষ্টি হয়। পরীক্ষায় দেখা যায়, যখন মাইক্রোওয়েভের ফ্রিকোয়েন্সি ঠিক দুটি শক্তিস্তরের ব্যবধানের সঙ্গে মিলে যায়, তখন সার্কিট সহজে তার ‘আটকে থাকা’ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসে। যত উচ্চতর শক্তিস্তর, তত দ্রুত এই ‘পলায়ন’ ঘটে। এই ধরনটি প্রমাণ করে, সার্কিটটি কেবল নির্দিষ্ট শক্তি প্যাকেট গ্রহণ বা নির্গমন করতে পারে। আর এটাই হচ্ছে তাদের গবেষণার সফলতা।
অপরদিকে কোয়ান্টাম টানেলিং হলো একটি কোয়ান্টাম যান্ত্রিক ঘটনা যেখানে একটি ইলেকট্রন বা পরমাণুর মতো একটি বস্তু একটি সম্ভাব্য শক্তি বাধার মধ্য দিয়ে যায় যা শাস্ত্রীয় বলবিদ্যা অনুসারে, বস্তুটির বাধা অতিক্রম করার বা অতিক্রম করার জন্য পর্যাপ্ত শক্তি না থাকার কারণে অতিক্রমযোগ্য হওয়া উচিত নয়। টানেলিং হলো পদার্থের তরঙ্গ প্রকৃতির একটি পরিণতি, যেখানে কোয়ান্টাম তরঙ্গ ফাংশন একটি কণা বা অন্যান্য ভৌত ব্যবস্থার অবস্থা বর্ণনা করে এবং শ্রোডিঙ্গার সমীকরণের মতো তরঙ্গ সমীকরণ তাদের আচরণ বর্ণনা করে। বাধার উচ্চতা, বাধার প্রস্থ এবং টানেলিং কণার ভরের সঙ্গে বাধার মধ্য দিয়ে তরঙ্গ প্যাকেটের সংক্রমণের সম্ভাবনা সূচকীয়ভাবে হ্রাস পায়, তাই টানেলিং সবচেয়ে বেশি দেখা যায় কম ভরের কণা যেমন ইলেকট্রন বা প্রোটন, যা মাইক্রোস্কোপিকভাবে সংকীর্ণ বাধার মধ্য দিয়ে টানেলিং করে। ইলেকট্রনের জন্য প্রায় ১-৩ এনএম (১-৩ হস) বা তার কম পুরুত্বের বাধা এবং প্রোটন বা হাইড্রোজেন পরমাণুর মতো ভারী কণার জন্য প্রায় ০.১ এনএম (০.১ হস) বা তার কম পুরুত্বের বাধা দিয়ে টানেলিং সহজেই শনাক্ত করা যায়। কিছু সূত্র বাধার মধ্যে তরঙ্গ ফাংশনের কেবল অনুপ্রবেশকে বর্ণনা করে, অন্যদিকে সংক্রমণ ছাড়াই, একটি টানেলিং প্রভাব হিসাবে, যেমন একটি সসীম বিভব কূপের দেয়ালে টানেলিং করা। পারমাণবিক নিউক্লিয়াসের নিউক্লিয়াস ফিউশন এবং আলফা তেজস্ক্রিয় ক্ষয়ের মতো ভৌত ঘটনাগুলিতে টানেলিং একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। টানেলিং অ্যাপ্লিকেশনগুলির মধ্যে রয়েছে টানেল ডায়োড, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং, ফ্ল্যাশ মেমোরি এবং স্ক্যানিং টানেলিং মাইক্রোস্কোপ। টানেলিং মাইক্রোইলেকট্রনিক্সে ব্যবহৃত ডিভাইসের ন্যূনতম আকার সীমিত করে, কারণ ইলেকট্রনগুলো সহজেই অন্তরক স্তর এবং ট্রানজিস্টরের মধ্য দিয়ে সুড়ঙ্গ করে যা প্রায় ১ এনএম-এর চেয়ে পাতলা হয়।
লেখক : অধ্যাপক, আইআইটি, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়