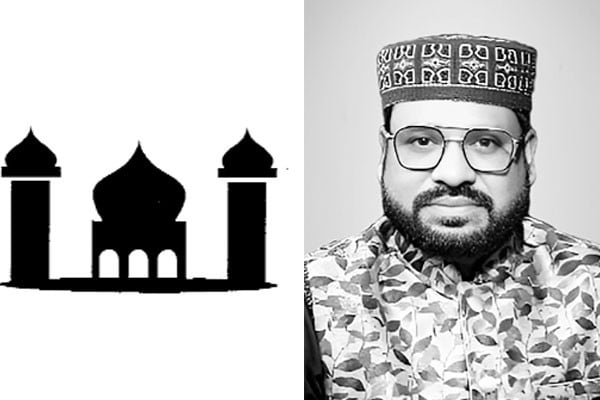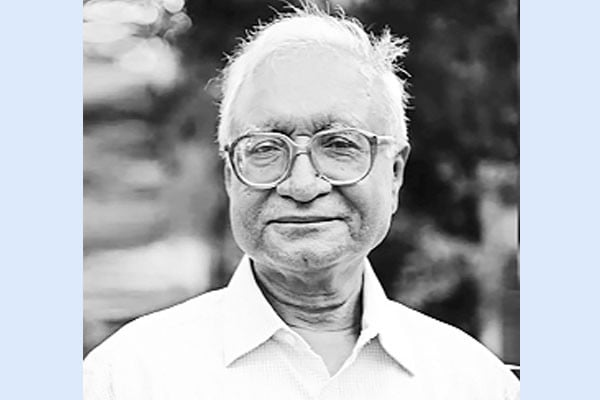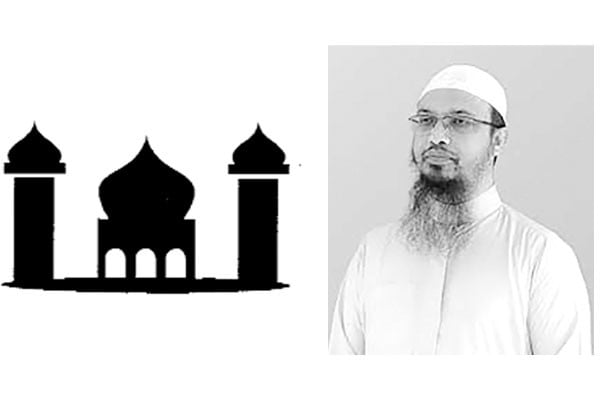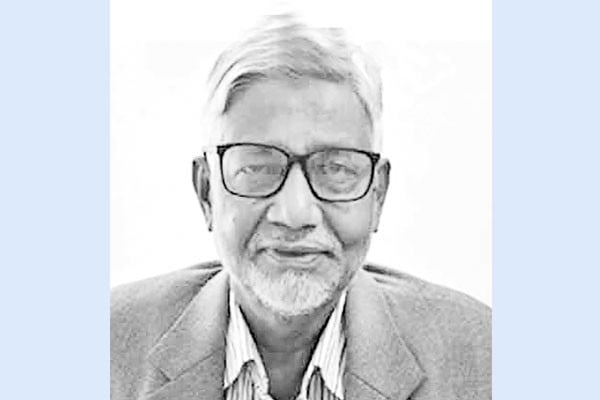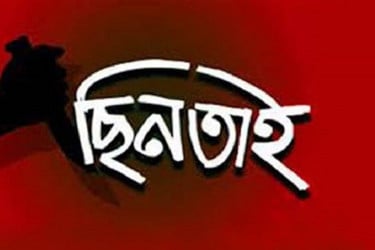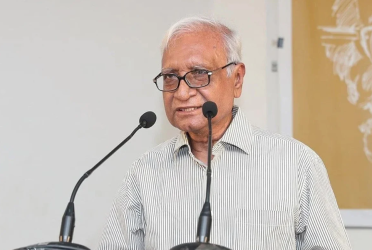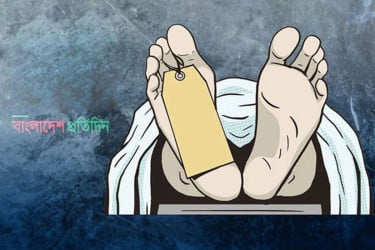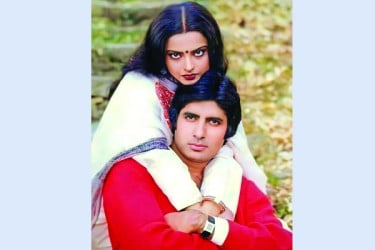একসময় ঢাকা ছিল প্রাণবন্ত, খোলা আকাশের নিচে আলো-বাতাসে ভরপুর এক পরিপাটি নগরী। দূরদূরান্ত থেকে আসা মানুষ এই শহরের প্রাণচাঞ্চল্যে মুগ্ধ হতো। কিন্তু সময়ের পরিক্রমায়, জীবনজীবিকার তাড়নায়, ক্রমে জনসংখ্যা বাড়ল, বাড়ল বিশৃঙ্খলা। একসময় এই প্রাণোচ্ছল শহর পরিণত হলো বর্জ্যরে নগরীতে। আজ ঢাকা মহানগরীর জনসংখ্যা ২ কোটিরও বেশি। আর সেই ২ কোটি মানুষের প্রতিদিনের ময়লায় হাঁপিয়ে উঠেছে শহরটি। মানুষ যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস যেন নগরবাসী হারিয়ে ফেলছেন। ২০১৬ সালে ঢাকা সিটি করপোরেশন শহরের বিভিন্ন রাস্তায় বসিয়েছিল প্রায় ১১ হাজার মিনি ডাস্টবিন। আশা জেগেছিল- এবার হয়তো চিত্র পাল্টাবে। কিন্তু বছর দুয়েকের মধ্যেই সেই ডাস্টবিনগুলো হারিয়ে গেল। একটা অনভ্যস্ত জনগোষ্ঠীকে অভ্যস্ত করা যে কত কঠিন, তা হাড়ে হাড়ে টের পেলেন সংশ্লিষ্টরা। অথচ এ শিক্ষা শুরু হওয়া উচিত পরিবার ও স্কুল থেকেই।
চীনে দেখেছি, প্রতিটি জায়গায়, এয়ারপোর্ট, হোটেল, বাসাবাড়ি, সব খানেই আলাদা দুটি ডাস্টবিন থাকে। একটিতে জৈববর্জ্য, অন্যটিতে অজৈব। জৈববর্জ্য ব্যবহার হয় বিদ্যুৎ ও সার উৎপাদনে, আর অজৈব বর্জ্য প্রক্রিয়াজাত হয়ে পরিণত হয় শিল্পের কাঁচামালে। ঢাকায়ও কিছু এনজিও এবং সিটি করপোরেশন এমন উদ্যোগ নিয়েছিল, কিন্তু ধারাবাহিকতার অভাবে তা টেকেনি। আজ সারা বিশ্বেই শিল্প ও কৃষিবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বড় চ্যালেঞ্জ। বিশেষ করে পোলট্রি খাতে। সঠিকভাবে বর্জ্য না সামলাতে পারলে পরিবেশ যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তেমনি মুরগিগুলোরও রোগ সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ে। তবে এখন অনেক খামারি পোলট্রি বর্জ্যকে জৈবসার বা কেঁচো সারের কাঁচামাল হিসেবে কাজে লাগাচ্ছেন। প্রায় এক যুগ আগে ঢাকার বেরাইদে একটি খামার এ ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। পুরোপুরি স্বয়ংক্রিয় না হলেও তাদের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ছিল কার্যকর উদ্যোগ। পোলট্রি বর্জ্য থেকে জৈবসার বা বায়োগ্যাস উৎপাদন পুরোনো খবর। বায়োগ্যাস নিয়ে কাজ করেছি বাংলাদেশ টেলিভিশনের ‘মাটি ও মানুষ’ অনুষ্ঠানে নব্বইয়ের দশকে। সে সময় বিটিভিতে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট নিয়ে ডজনখানেক প্রতিবেদন প্রচার হয়েছিল। ফলে একটা বিশাল জনগোষ্ঠী উপকৃত হয়েছে। সে সময় গ্রামীণ গৃহস্থালির জ্বালানির সংকট ছিল। এখন গ্যাস সিলিন্ডার চলে গেছে প্রত্যন্ত গ্রামের বাড়িতেও। নব্বইয়ের দশকে যখন বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট বিষয়টাকে তুলে ধরা হলো, তখন মানুষের মাঝে বেশ আগ্রহ তৈরি হয়েছিল। একটা গৃহস্থ পরিবারে যদি পাঁচটি গরু থাকে, সেই গরুর প্রতিদিনের যে গোবর আসে, সেই গোবর থেকে বায়োগ্যাস প্ল্যান্টের মাধ্যমে দুবেলা রান্না, বিদ্যুতায়নের পাশাপাশি পাওয়া যায় স্লারি, যা উৎকৃষ্টমানের জৈবসার। সেই প্রতিবেদনগুলো প্রচারের পর প্রচুর চিঠি আসত বিস্তারিত জানার জন্য। বিসিএসআইআরের জ্বালানি গবেষণা ও উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরে দেখেছিলাম বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট নির্মাণের অসংখ্য নির্দেশিকা। সেগুলো নিয়ে অনুষ্ঠানের এক পর্বে বলে দিই, যারা বিস্তারিত জানতে চান, তারা যেন চিঠির সঙ্গে নিজের ঠিকানাসহ ডাকটিকিট-সংবলিত একটা খালি খাম পাঠান। প্রতিদিন হাজার হাজার চিঠি আসত। আমরা খুব যত্নে সেগুলোর জবাব দিতাম।
এ সময়ের ভিতর পৃথিবী বদলেছে অনেকখানি। হাজারগুণ গতিতে এগিয়েছে বিজ্ঞান। কিন্তু জৈব জ্বালানির বিকল্প পরিবেশবান্ধব ও নিরাপদ কোনো প্রযুক্তি এখনো আবিষ্কৃত হয়নি; যার কারণে উন্নত দেশগুলোও জৈব পাওয়ার প্ল্যান্ট থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের দিকে ঝুঁকেছে। এর গুরুত্বপূর্ণ দুটি দিক আছে। এক. বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। দুই. জাতীয় গ্রিডে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বিদ্যুৎ যুক্ত করা সম্ভব হচ্ছে।
আশির দশকের মাঝামাঝি একটি বাণিজ্যিক গ্রুপের এক অঙ্গপ্রতিষ্ঠান ঢাকার পৌর বর্জ্য থেকে জৈবসার তৈরির চেষ্টা চালিয়েছিল। কৃষিবিদ ড. সদরুল আমিন সেই প্রকল্পে কাজ করতেন। তাঁর অনুরোধে ‘মাটি ও মানুষ’-এ প্রচার করেছিলাম বিষয়টি। তখন মনে হয়েছিল, এবার হয়তো মিউনিসিপ্যাল বর্জ্য সম্পদে রূপ নেবে। কিন্তু এত বছরেও সেই আশার আলো দেখা যায়নি। পৃথিবীর বহু দেশ যেখানে বর্জ্যকে সম্পদে রূপ দিয়েছে, সেখানে আমরা এখনো আবর্জনার পাহাড়ে বসবাস করছি।
২০০৫ সালে জাপানের মরিওকার কইওয়াই অর্গানিক ফার্মে গিয়ে প্রথম বড় আকারের বায়োগ্যাস প্ল্যান্টের প্রতিবেদন ধারণ করেছিলাম। পরে ২০১৬ সালে ‘হৃদয়ে মাটি ও মানুষ’-এ দেখিয়েছিলাম জার্মানির জেলসনের একটি জৈব বিদ্যুৎ কেন্দ্র, যেখানে কম গুরুত্বের শস্যদানা দিয়েই বিদ্যুৎ তৈরি হয়। ২০১৮ সালে একটি পোলট্রি ফার্ম স্থাপন করে দেশের প্রথম বড় জৈব পাওয়ার প্ল্যান্ট, যেখানে প্রতিদিন আড়াই লাখ পোলট্রির বর্জ্য থেকে উৎপাদিত হয় ৩৫০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ। ওই প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী বলেছিলেন, আগে এসব বর্জ্য সামলাতে বিপাকে পড়তেন। পরে ‘হৃদয়ে মাটি ও মানুষ’-এর প্রতিবেদন দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি জৈব বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট স্থাপন করেন। এখন তার খামারের ২৪ ঘণ্টার বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণ হয় এই প্ল্যান্ট থেকেই। পাশাপাশি উৎপাদিত সার কাজে লাগে বিভিন্ন ফল ও ফসল চাষে। পুরো ব্যবস্থাই স্বয়ংক্রিয়, তাই শ্রমিক খরচও প্রায় শূন্য। একই ধরনের দৃশ্য দেখেছি জার্মানির জেলসনে ও চীনের শ্যাংডং প্রদেশে। বিশাল শিল্পপ্রতিষ্ঠান চালাচ্ছে এক-দুজন মানুষ-পুরোপুরি স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায়। সেখানে পোলট্রি খামারগুলোও বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে সম্পূর্ণ শিল্পভিত্তিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে।
সম্প্রতি গাজীপুরের শ্রীপুরে একটি প্রতিষ্ঠানে দেখেছি, তারাও পোলট্রি বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ ও জৈবসার উৎপাদন করছে। তাদের উৎপাদিত সার আবার একটি বেসরকারি কোম্পানি কিনে নিজস্ব ব্র্যান্ডে বাজারজাত করছে। বড় খামারগুলো যদি এই ব্যবস্থা অনুসরণ করে, তাহলে নিজেদের উৎপাদিত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডেও যোগ করতে পারবে। যশোরেও এডিবির সহায়তায় কয়েক বছর আগে শুরু হয়েছে বর্জ্য থেকে সার ও বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প। সেখানে পৌর বর্জ্য থেকেই তৈরি হচ্ছে জৈবসার এবং বায়োগ্যাস থেকে বিদ্যুৎ। সেই বিষয়টিও খুব আশাব্যঞ্জক। বিশ্বব্যাপী এখন কৃষি ব্যবস্থাপনা মিশে গেছে শিল্প ব্যবস্থাপনার সঙ্গে। কৃষিশিল্প উদ্যোক্তারা চেষ্টা করছেন, একটি উপকরণ থেকে যেন একাধিক শিল্পপণ্য তৈরি হয়। প্রযুক্তি ও যন্ত্রের উন্নত ব্যবহারে সেটা এখন অনেক সহজও হয়েছে। শুধু পোলট্রি নয়, সব ধরনের জৈববর্জ্য থেকেই সম্ভব নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদন। সবার সচেতনতায় বর্জ্যই হতে পারে অমিত সম্ভাবনার উৎস। এর মাধ্যমে তৈরি হতে পারে বিদ্যুৎ, সার, কর্মসংস্থান। মাটির হারানো উর্বরতা ফিরিয়ে আনতে জৈবসারই কৃষকের ভরসা। তাই বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অভ্যাস গড়ে তোলা এখন সময়ের দাবি। তাতে নিশ্চিত হবে পরিচ্ছন্নতা, বাঁচবে পরিবেশ, আর খুলে যাবে টেকসই উন্নয়নের নতুন দরজা।
লেখক : মিডিয়া ব্যক্তিত্ব