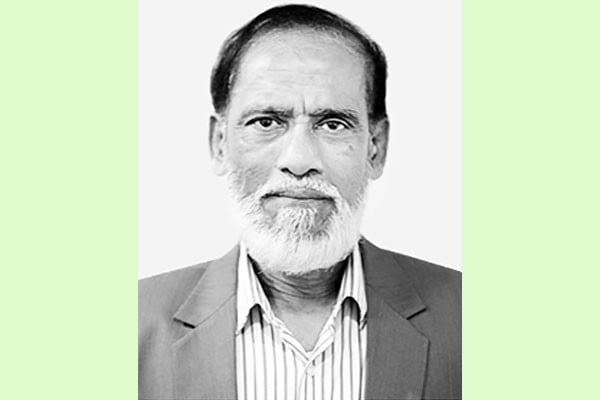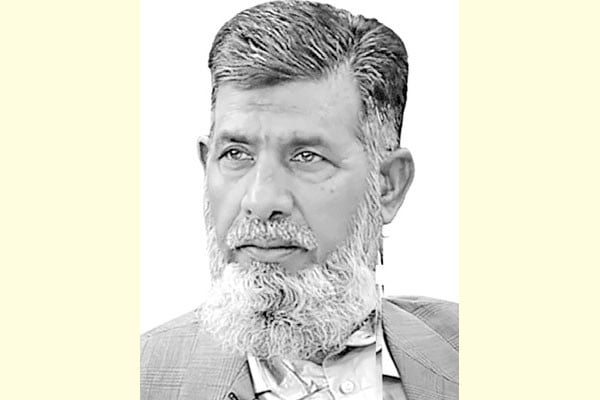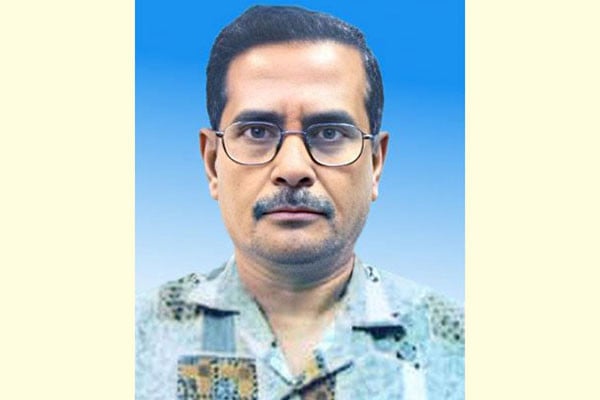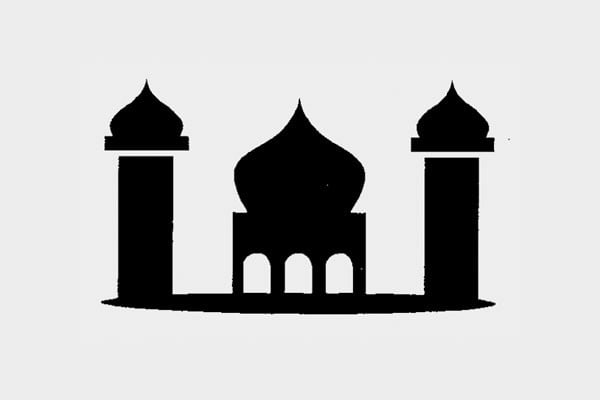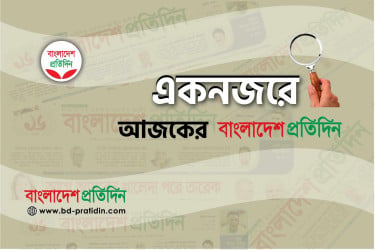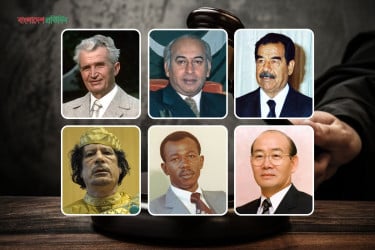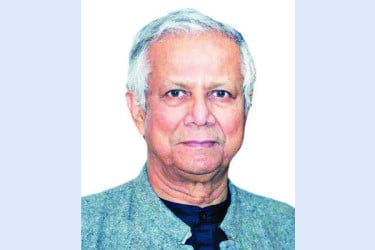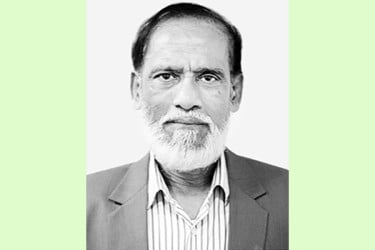অ্যাডভোকেট আবদুল জব্বার ছিলেন পাকিস্তান আমলে খুলনার বাম রাজনীতির প্রাণপুরুষ। মওলানা ভাসানীর ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (ন্যাপ) কেন্দ্রীয় কমিটির সিনিয়র সহসভাপতি। হুজুর ভাসানীর বিশ্বস্ত ও প্রিয় পাত্র হিসেবে বিবেচিত হতেন তিনি। ব্রিটিশ আমলে অ্যাডভোকেট জব্বার কংগ্রেসের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। কংগ্রেসের শীর্ষ নেতা মাওলানা আবুল কালাম আজাদেরও খুবই কাছের লোক ছিলেন তিনি। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে শহীদ হন এই প্রথিতযশা আইনজীবী।
অ্যাডভোকেট আবদুল জব্বারের একনিষ্ঠ শাগরেদ ছিলেন আমার এক মামা। তাঁর সঙ্গে বেশ কয়েকবার ন্যাপের ওই শীর্ষনেতার বাসভবনে যাওয়ার সুযোগ হয়েছে। জব্বার সাহেব বলতেন, তিনি রাজনৈতিক গুরু হিসেবে দুই মাওলানাকে পেয়েছেন। এদের একজন মাওলানা আবুল কালাম আজাদ। অন্যজন হুজুর ভাসানী। মাওলানা আজাদ ছিলেন হুজুর ভাসানীরও নেতা। অবিভক্ত ভারতবর্ষের শীর্ষ আলেমদের একজন। কংগ্রেসের সভাপতি পদেও অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন তিনি। মওলানা ভাসানীর পরিচিতি ছিল পীর হিসেবে। ধর্মীয় নেতা হিসেবে পরিচিতি গড়ে উঠলেও তারা দুজনই ছিলেন আক্ষরিক অর্থেই অসাম্প্রদায়িক। ধর্ম ও রাজনীতিকে তারা কখনো এক ঝুলিতে ভরেননি। অ্যাডভোকেট আবদুল জব্বার দুঃখ করে বলতেন, কংগ্রেসের অন্য নেতারা মাওলানা আবুল কালাম আজাদের মতো অসাম্প্রদায়িক হলে সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে ভারত ভাগের প্রয়োজন হতো না।
মুক্তিযুদ্ধে আমাদের এক সহযোদ্ধা আবদুল্লাহ ছিলেন মাদ্রাসার ছাত্র। তাঁর বাবা ছিলেন নোয়াখালীর এক মসজিদের ইমাম। মাওলানা আজাদের ভাবশিষ্য। ছিলেন জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সদস্য। পাকিস্তান আমলে মুফতি মাহমুদের নেতৃত্বাধীন জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের কর্মী। তিনি বলতেন, কোরআনের ভাষা আরবি। জান্নাতের ভাষাও আরবি। আরবি ভাষায় পাকিস্তান উচ্চারণ করা যায় না। কারণ সে ভাষায় ‘প’ জাতীয় কোনো অক্ষর নেই। মুফতি মাহমুদের দল পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশে বেশ জনপ্রিয়। ১৯৭২ সালে তিনি ওই প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হন। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের যেসব দল শেখ মুজিবের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের পক্ষে ছিল জামিয়াতে উলামায়ে ইসলাম তাদের অন্যতম। ভুট্টোর হুমকি অগ্রাহ্য করে ১৯৭১ সালের মার্চে মুফতি মাহমুদ ঢাকা সফর করেন। কৌশলগত কারণে জামিয়াতে উলামায়ে ইসলামের পাকিস্তানি শাখা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে নীরব থাকতে বাধ্য হয়। তবে ওই দলের বাংলাদেশি আলেমদের কেউ কেউ মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। যাঁদের অন্যতম মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসঊদ।
পাকিস্তানে এখনো সবচেয়ে জনপ্রিয় ইসলামি দল জামিয়াতে উলামায়ে ইসলাম। যার নেতৃত্বে মুফতি মাহমুদের পুত্র মাওলানা মুফতি ফজলুর রহমান। যিনি বাংলাদেশ সফরে আসেন ১৪ নভেম্বর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অনুষ্ঠিত খতমে নবুয়ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে।
 বলছিলাম মাওলানা আজাদের কথা। তাঁর পুরো নাম আবুল কালাম মহিউদ্দিন আহমেদ। আজাদ ডাকনাম। তিনি ছিলেন ভারতবর্ষের শীর্ষস্থানীয় স্বাধীনতাসংগ্রামী। স্বাধীন ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী। দক্ষিণ এশিয়াজুড়ে মাওলানা আবুল কালাম আজাদ নামেই তিনি বেশি পরিচিত। তিনি ছিলেন তাঁর সময়ের অন্যতম সেরা আলেম। তাঁর পূর্বপুরুষরা ছিলেন আফগানিস্তানের হেরাতের অধিবাসী। ভারতবর্ষে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবরের আমলে তাঁরা ভারতে আসেন। প্রথমে আগ্রায় ও পরবর্তীকালে দিল্লিতে থিতু হন। মোগল দরবারের শীর্ষ আলেম ছিলেন আজাদের পূর্বপুরুষরা।
বলছিলাম মাওলানা আজাদের কথা। তাঁর পুরো নাম আবুল কালাম মহিউদ্দিন আহমেদ। আজাদ ডাকনাম। তিনি ছিলেন ভারতবর্ষের শীর্ষস্থানীয় স্বাধীনতাসংগ্রামী। স্বাধীন ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী। দক্ষিণ এশিয়াজুড়ে মাওলানা আবুল কালাম আজাদ নামেই তিনি বেশি পরিচিত। তিনি ছিলেন তাঁর সময়ের অন্যতম সেরা আলেম। তাঁর পূর্বপুরুষরা ছিলেন আফগানিস্তানের হেরাতের অধিবাসী। ভারতবর্ষে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবরের আমলে তাঁরা ভারতে আসেন। প্রথমে আগ্রায় ও পরবর্তীকালে দিল্লিতে থিতু হন। মোগল দরবারের শীর্ষ আলেম ছিলেন আজাদের পূর্বপুরুষরা।
১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের পর ভারতবর্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে মোগল শাসনের অবসান ঘটে। শেষ সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে বার্মার রেঙ্গুনে নির্বাসন দেওয়া হয়। মাওলানা আজাদের বাবা খায়েরউদ্দিন সে প্রতিকূল অবস্থায় ভারত ছেড়ে মক্কায় চলে যান। সেখানেই বসবাস করেন তিনি। মক্কার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের মেয়েকে বিয়ে করেন। ১৮৮৮ সালের ১১ নভেম্বর পবিত্র মক্কা নগরীতে মাওলানা আজাদের জন্ম। পুত্রসন্তানের বাবা হওয়ার দুই বছর পর ১৮৯০ সালে খায়েরউদ্দিন সপরিবার কলকাতায় চলে আসেন। আজাদের পরিবার কলকাতাতেই স্থায়ী হয়। খায়েরউদ্দিন নিজে ছিলেন সুশিক্ষিত। সে সময়ে কলকাতা বা ভারতবর্ষের প্রচলিত স্কুল কিংবা মাদ্রাসা শিক্ষায় আজাদের বাবার তেমন আস্থা ছিল না। তাই তিনি বাড়িতেই আজাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। বাড়িতে তিনি মাতৃভাষা আরবিতে গণিত, জ্যামিতি, দর্শন সম্পর্কে শিক্ষা নেন।
তরুণ বয়সে মাওলানা আজাদ ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য বিপ্লবী চিন্তাধারার দিকে ঝুঁকে পড়েন। অরবিন্দ ঘোষ এবং শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর মতো বিপ্লবী নেতাদের সংস্পর্শে বিপ্লবী রাজনীতিতে দীক্ষা নেন। ভাবেন সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমেই কেবল দেশের স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব।
দেশবাসীকে স্বাধীনতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করতে ‘আল হিলাল’ নামের একটি উর্দু পত্রিকা প্রকাশ করেন মাওলানা আজাদ। এই পত্রিকার মাধ্যমে তিনি ব্রিটিশবিরোধী মনোভাব মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেন। অল্প দিনেই পত্রিকাটি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। মাওলানা আজাদ সম্পাদিত ‘আল হিলাল’-এর জনপ্রিয়তা দেখে ব্রিটিশ সরকার তড়িঘড়ি করে পত্রিকাটি বাজেয়াপ্ত করে। তত দিনে সাংবাদিকতায় মাওলানা আজাদের সুনাম ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। তিনি ‘আল বালাঘ’ নামে আরও একটি পত্রিকা চালু করেন। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার সেটিও বাজেয়াপ্ত করে। মাওলানা আজাদ ১৯২০ সালে খিলাফত আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। এ আন্দোলনের সূত্র ধরে তিনি মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে পরিচিত হন এবং তাঁর অসহযোগ আন্দোলনেও জড়িয়ে পড়েন। অচিরেই মাওলানা আজাদ শীর্ষ পর্যায়ের কংগ্রেস নেতাদের একজন হয়ে ওঠেন। ১৯২৩ সালে মাত্র ৩৫ বছর রয়সে তিনি ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন।
১৯৩৯ সালে শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। জাপানি বাহিনী ভারত সীমান্তে বার্মা পর্যন্ত চলে আসে। যুদ্ধে সরকারকে সমর্থন দানের প্রশ্নে কংগ্রেস দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ে। কঠিন সময়ে মাওলানা আজাদ আবার কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৪০ থেকে ’৪৬ পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্ব পালন করেন।
অহিংসবাদী মহাত্মা গান্ধী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ব্রিটিশদের সহায়তা করার বিরুদ্ধে ছিলেন। শুনতে বেশ ভালো লাগলেও তা বাস্তবসম্মত ছিল না। মাওলানা আজাদের তত্ত্ব ছিল ‘যদি ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষের স্বাধীনতা দেয়, তবে কংগ্রেসের উচিত যুদ্ধে ব্রিটিশদের পক্ষে যোগ দেওয়া।’ তিনি বিশ্বাস করতেন, ‘দেশের ভিতরের স্বাধীনতা সংগ্রাম আর বাইরের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়াই, এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। ...এই দুটি বিষয়কে গুলিয়ে ফেলা ঠিক নয়।’
মাওলানা আজাদ মনেপ্রাণে ছিলেন দেশভাগের বিরোধী। অসাম্প্রদায়িক স্বাধীন ভারতবর্ষ অর্জনে তিনি নিরলস চেষ্টা চালান। নেহরু, প্যাটেলসহ কংগ্রেস নেতাদের সংকীর্ণ মনোভাবে তিনি আহত হন। ১৯৩৬ সালে বোম্বাইয়ে পার্শি সম্প্রদায়ের নারিমান ছিলেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় নেতা। তাঁকে মুখ্যমন্ত্রী করা হবে এমনটিই ভাবা হতো। সরদার প্যাটেল ও তাঁর সহযোগীরা মুখ্যমন্ত্রী করেন একজন হিন্দু নেতাকে। বিহারে কংগ্রেসের সবচেয়ে বড় নেতা ছিলেন ডা. সৈয়দ মাহমুদ। তিনি সর্বভারতীয় কংগ্রেসেরও সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। কিন্তু তাঁকে বঞ্চিত রাখা হয় তিনি মুসলমান এই অপরাধে। অখণ্ড স্বাধীন ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পক্ষপাতী ছিলেন মাওলানা আজাদ। যে ব্যবস্থায় পররাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা ও যোগাযোগ কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকত। প্রদেশগুলো পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের অধিকারী হতো। এ প্রস্তাবে গান্ধীরও সমর্থন ছিল। ১৯৪৬ সালে ব্রিটিশ সরকারের পাঠানো কেবিনেট মিশনের প্রস্তাবে ভারতের তিনটি প্রধান অঞ্চলে স্বায়ত্তশাসন রেখে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার গঠনের কথা বলা হয়। মুসলিম লীগ এ প্রস্তাবের পক্ষে ছিল। কিন্তু কংগ্রেস নেতারা উদার হতে পারেননি।
ভারতভাগের প্রস্তুতি নিয়ে লর্ড মাউন্টব্যাটেন যখন ভারতবর্ষে আসেন, তখনও মাওলানা আজাদ তা ঠেকাতে চেষ্টা করেন। কিন্তু নেহরু ও প্যাটেলের মতো কংগ্রেস নেতারা তখন ভারতভাগের জন্য ছিলেন উন্মুখ। তাঁদের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলেছেন ভারত ভঙ্গের পরিণাম নিয়ে। তত দিনে গান্ধীও চলে গেছেন নেহরু-প্যাটেলদের দলে। মাওলানা আজাদের পক্ষে মনঃকষ্টে ভুগতে হয়েছে সে সময়। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ বিভক্ত হয় দুই দেশে। মাওলানা আজাদ ভারতের শিক্ষামন্ত্রী হন। তিনি পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের তত্ত্ব তুলে ধরেন। বলেন, তাতেই দুই দেশের মঙ্গল।
দুই.
১৭ নভেম্বর ছিল মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর ৪৯তম মৃত্যুবার্ষিকী। হুজুরের খুব কাছের একজনের উদ্ধৃতি দিয়ে লেখাটি শেষ করতে চাই- ‘মওলানা হুজুর হঠাৎ দেখতে পেলেন, প্ল্যাটফরমে স্টেশনমাস্টার ছাড়া আর একটি লোক আছে। তাকে জোরেশোরে ডাকলেন কাছে আসতে। লোকটি বয়সে তরুণ। স্বাস্থ্য একেবারে লিকলিকে। তাকে কাছে ডেকে বললেন, তুমি গোয়েন্দা বিভাগের লোক, তাই না? লোকটি হ্যাঁ বলল না, তবে কাচুমাচু করতে লাগল। বললেন, আরে বাবা, তোমার ডিউটি তুমি করে যাও। আমাকে দেখিয়ে বললেন, এ হলো আমার সেক্রেটারি। খবরাখবর আমি গোপন রাখি না। অযথাই তোমরা হয়রান হবে কেন? যা জিজ্ঞেস করার আমাকে বা সেক্রেটারিকে করো। আমরা সহযোগিতা করব। মিথ্যা কথা লিখবা না। সত্য লিখবা। লিখবা, এই সম্মেলন জঙ্গি মেজাজের হবে কমিউনিস্টদের সব গ্রুপ আসবে না। লোকটাকে মওলানা ঘাবড়ে দিলেন একটি কথা বলে। বললেন, সম্মেলনের লোকজনকে খিচুড়ি খাওয়ানো হবে। সেজন্য সরকারকে লিখেছি, সুন্দরবনের নিলাম ডাকের ব্যবহারের অযোগ্য লাকড়ি আমাকে দিতে। আমি কিনে নেব। মালবাহী ট্রেনে ২/৪ দিন পর পাঁচবিবি পৌঁছাবে। ইয়াহিয়া খানের সরকার যদি মার্শাল ল’র দোহাই দিয়ে সম্মেলন পণ্ড করতে চায় তাহলে ওই লাকড়িই হয়ে যাবে হাতের লাঠি। পুলিশ ঠেকাতে পারবে না। জঙ্গি মিছিল পুলিশকে আক্রমণ করবে। তাই বলি জানাও, আমাদের শান্তিপূর্ণভাবে সম্মেলন করতে দেওয়া হোক। আমরা আক্রমণাত্মক হব না। আমরা আক্রমণাত্মক হব জুন মাসে। ঘুষ লালনপালনের আখড়াগুলো আক্রমণ করব। সাবরেজিস্ট্রারের অফিস, থানা অফিস, সিও রেভিনিউর অফিস কৃষককে শুধুই হয়রানি করে। সমাজের চরিত্র বদলাতে হবে। তাই এসবের খোলনলচে পাল্টাতে হবে। বুঝেছ কি বলতে চেয়েছি? তুমি কী বুঝবা? তোমার হাইর্যাঙ্কের অফিসারদের বোঝাতে পারি না। লোকটির প্রতি মায়াই হলো। হয়তো মাত্র কয়েক মাস হলো চাকরি হয়েছে, সে মওলানাকে কীভাবে চিত্রিত করবে। তার হয়তো ডিউটি ছিল, মওলানা ভাসানী পৌঁছেছেন কিনা, তা রিপোর্ট করা। সে এখন আটকে গেল জাতীয় রাজনীতিতে। কারণ দেশে মার্শাল ল’। এহেন সম্মেলন করার অনুমতি দেওয়া যায় না। কে শুনবে কার কথা। মওলানা তখন প্রশ্ন ওঠাবেন, তাহলে শাহপুরে যে মাস ছয়েক আগে সম্মেলন করলাম, তার চরিত্র তো একই ছিল। ঢাকাতে পারনি। মহিপুর একই। ঠেকাতে পারবা না। আমি করবই। গোয়েন্দা লোকটি এখন সটকাতে পারলে বাঁচে। এই ফাঁকে আমি একটু সেক্রেটারিগিরি করলাম। বললাম, যান, চলে যান। পরবর্তী সময়েও আমাদের পাবেন। ঠিক তখনই মওলানা হুজুর বললেন, বারী যাও তুমি চা-বিস্কুট খেয়ে আসো। আমার জন্যও নিয়ে এসো। স্টেশনমাস্টার বললেন, হুজুর আমার রুমে চলেন। সব আনাচ্ছি। গোয়েন্দাও বলল, হুজুর আমি চা নিয়ে আসি। মওলানা বললেন, বাইরে বসাতে আরাম পাচ্ছি। সকালের ঝিরঝির বাতাস। গোয়েন্দাকে বললেন, তুমি আনতে পারো কিন্তু পয়সা দিবা না। বারী পয়সা দেবে। তাই হয়েছিল। গোয়েন্দাটি দূরে গেলে মওলানা বললেন, এদের স্বল্প বেতন। এদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য কর না। সে খুব ঘাবড়ে গেছে। সহজ করতে চা আনতে বললাম। মাস্টার, তোমার রুমে আমি বিশ্রাম নিলে উপরস্থ অফিসার তোমাকে শোকজ করে না? স্টেশনমাস্টার বললেন, না হুজুর, তারা বরং বলেন, মওলানা সাহেবকে সেবা দেবেন। ওনার চোটপাটে পশ্চিমা অফিসাররা একটু হলেও থেমে থাকে।’ মওলানা ভাসানীকে কাছে থেকে দেখা : সৈয়দ ইরফানুল বারী)।
লেখক : সিনিয়র সহকারী সম্পাদক, বাংলাদেশ প্রতিদিন
ইমেইল : [email protected]