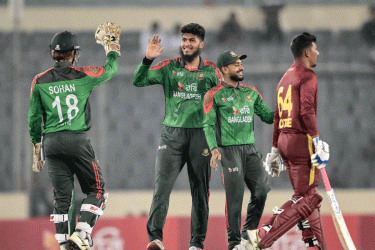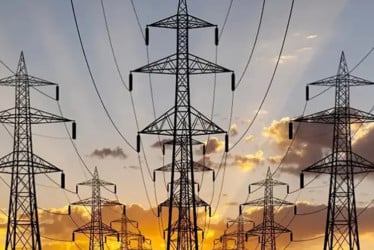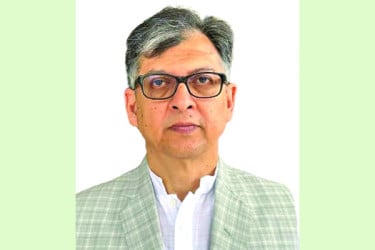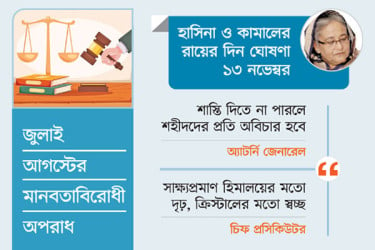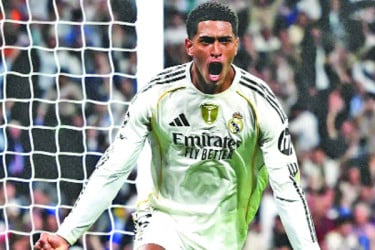ভারতের উত্তর প্রদেশে নদীয়া জেলা শহরের মতো আলোকসজ্জা না থাকলেও তেহট্ট মহকুমার সীমান্তের পুজামণ্ডপগুলোতে আছে আবেগ আর নিষ্ঠা। এর মধ্যে রয়েছে বেশ কিছু প্রাচীন পুজামণ্ডপও। সেই সব পুজামণ্ডপের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে নানা লোককথাও।
তেহট্টের ভট্টাচার্য বাড়ির পূজামণ্ডপ এ বছর ৪০৮ বছরে পড়ল। ভট্টাচার্য বাড়ির সদস্য জগদীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য জানান, ১০১৩ বঙ্গাব্দে সিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য ওই পূজা শুরু করেন। পরে তার নাতি তন্ত্রসাধক জগবন্ধু ভট্টাচার্য পঞ্চমুণ্ডের আসনে তান্ত্রিক মতে দুর্গা পূজা করতেন। মহাষ্টমীর দিন মোষ ও পরে পাঁঠা বলি দেওয়া হত। কোনও এক বছর বলির সময়ে লাল রক্তের বদলে সাদা রক্ত দেখা গেলে পশু বলি বন্ধ করে দেওয়া হয়। তারপর থেকে ক্ষীরের তৈরি পাঁঠা বলি দেওয়া হয়। উল্টো রথের দিন প্রতিমার কাঠামো বাঁধা ও জন্মাষ্টমীর দিন কাঠামোয় মাটির প্রলেপ লাগিয়ে প্রতিমা তৈরির কাজ শুরু হয়। এখনও সপ্তমীতে নবপত্রিকাকে পালকি করে নদীতে স্নান করাতে নিয়ে যাওয়া হয়। এখানে দেবীর বাহন সিংহ দেখতে ঘোড়ার মতো। রং সাদা।
করিমপুর-২ ব্লকের দোগাছি গ্রামে রাজবল্লভীর পূজা শুরু হয়েছিল প্রায় ৩০০ বছর আগে। কথিত আছে নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে রাজবল্লভ নামে এক জেলের জালে উঠে আসে কষ্টিপাথরের দুর্গা ও বিষ্ণু মূর্তি। রানি ভবানী ওই পুজো শুরু করেন। এখন অবশ্য ওই পূজা সর্বজনীন। এলাকার সকলেই ওই পূজাতে মেতে ওঠেন।
এ বছর ৪০০ বছরে পা দিল ধোড়াদহের চৌধুরী বাড়ির পুজো। পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, আগে পূজা উপলক্ষে মেলা বসলেও এখন তা বসে না। তবে জৌলুস হারালেও পূজা হয় প্রাচীন নিয়ম মেনেই। কথিত আছে ১৫৭৬ সালে দিল্লির মোগলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন যশোরের রাজা বারো ভুঁইয়ার অন্যতম প্রতাপাদিত্য। মোগলদের হাত থেকে নিজের শিশুপুত্রকে বাঁচাতে দেওয়ান দুর্গারাম চৌধুরীকে অনুরোধ করেছিলেন। সেই মতো দুর্গারাম শিশুটিকে নিয়ে অবিভক্ত বাংলার বনজঙ্গলে ঢাকা ধোড়াদহে লুকিয়ে ছিলেন। পরে যুদ্ধ শেষে ফিরিয়ে দেন প্রতাপাদিত্যের শিশুপুত্রকে। খুশি হয়ে প্রতাপাদিত্য দুর্গারামকে পাঁচটি মহল দান করেন। সেই সময় থেকেই জঙ্গল কেটে আট চালার ঘরে দুর্গারাম শুরু করেন দুর্গাপুজো। পলাশির যুদ্ধের চার বছর আগে ১৭৫৩ সালে সেই আট চালার ঘর ভেঙে তৈরি হয় পাকা মন্দির। তারপর থেকে আজও সেই রীতি মেনেই পুজো হয়ে আসছে।
যমশেরপুর বাগচীবাড়ির পূজামণ্ডপও এলাকার প্রাচীন পূজামণ্ডপ বলে পরিচিত। আনুমানিক ১২৪৫ সালে ওই পূজা শুরু হয়েছিল। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, করিমপুরের পাশেই যমশেরপুরের এই পূজা না দেখলে অনেক কিছুই বাকি থেকে যায়।
সীমান্তবর্তী করিমপুরে একটা সময় হাতেগোনা কয়েকটি দুর্গাপূজা হত। বর্তমানে করিমপুরে ৪০ টিরও বেশি পুজো হয়। শিকারপুর সীমান্তেও প্রায় ১২টা পুজো হয়। তার মধ্যে শুধু বাজারেই হয় ৩টি পূজা। এখানে দশমীর দিন বেশিরভাগ প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয় স্থানীয় মাথাভাঙা নদীতে। প্রতিমা নিরঞ্জনের সময় নদীর দুই পাড়ে হাজির হন দুই বাংলার মানুষ।
শিকারপুরের শিবেন সাহা পূজামণ্ডপের কথা বলতে গিয়ে নস্টালজিক হয়ে পড়েন। তিনি বলেন, “আমাদের ছোটবেলার দেখা সেই পূজামণ্ডপ এখন আর নেই। তখন তো সীমান্ত বলে এরকম কিছু ছিল না। ঈদ, পূজা কিংবা অন্য উৎসবের সময় দু’দেশে আমাদের অবাধ যাতায়াত ছিল। তখন পূজাও ছিল অন্যরকম। এখন অবশ্য দিন বদলালেও সীমান্তের পূজা নিয়ে সেই আবেগ কিন্তু একইরকম আছে।
বিডি-প্রতিদিন/৩ অক্টোবর, ২০১৪/মাহবুব

_34671.jpg)


-24-10-2024.jpg)





-kuakata-11-10-2024.jpg)