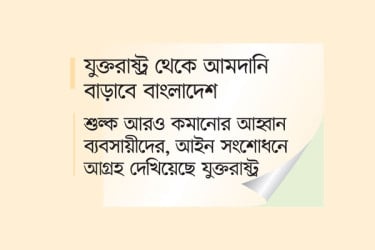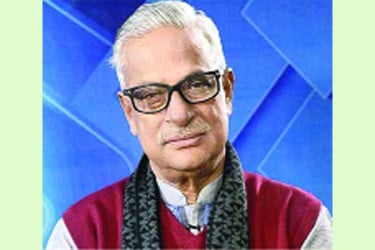বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) কেবল একজন ব্যক্তি বা একক কবিসত্তা নন, তিনি একটি যুগের প্রতিভূ। বাঙালির জাতীয় জীবনে একাধিক যুগপ্রবাহকে তিনি ব্যক্তি সাধনায় ধারণ ও বহন করে ফিরেছেন। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে একাধিক যুগধারাকে তিনি রূপ দিয়েছেন তাঁর বিচিত্র রচনাসম্ভারে। ‘রবীন্দ্রনাথ যুগমানব নন, সমকালীন বাঙালি জীবন-ধর্মের মহাঅধিনায়ক তিনি। সেই নায়কতার ভূমিকা বহুলার্থক সম্ভাবনা নিয়ে অপেক্ষা করেছে ইতিহাসের ফলকে। তাই সমগ্র রবীন্দ্র রচনাবলির ঐতিহাসিক পরিচয় একটি মাত্র পর্যায়সীমার মধ্যে বেঁধে রাখা অসম্ভব।’ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-১৮৯৪) হাত ধরে যেমন বাংলা উপন্যাসের জন্ম ও বিকাশ; তেমনি রবীন্দ্রনাথের হাতে ছোটগল্পের উৎপত্তি, বিকাশ ও পরিণতি লাভ করেছে। একটা সময় বাঙালি পাঠকরা মনে করতেন, ‘ছোটগল্পকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে লিখলে উপন্যাস হয় এবং উপন্যাসের ডালপালা ছেঁটে দিয়ে ছোট করে দিলে ছোটগল্প হয়। এ মত একেবারে ভ্রান্ত। ছোটগল্প ও উপন্যাসের ধরন-ধারণ ও রীতিপ্রকরণ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সে যাই হোক, রবীন্দ্রনাথই প্রথম সচেতনভাবে ছোটগল্প লিখতে প্রবৃত্ত হন, তিনিই এর পথনির্মাতা, আবার তিনিই এর শ্রেষ্ঠ শিল্পী।’ ১২৮৪ বঙ্গাব্দে ‘ভারতী’ পত্রিকায় কিশোর বয়সে সদ্য কবি হিসেবে খ্যাতি পাওয়া বরীন্দ্রনাথ ভিখারিণী নামে প্রথম ছোটগল্প লিখেছিলেন। প্রথম গল্পের প্লটে মানবজীবনের রূঢ় ও বাস্তব চেহারার প্রেক্ষণা না থাকলেও কিশোর মনের পরিপূর্ণ ভাবোচ্ছ্বাস ও বিষাদ-বেদনা সুনিপুণভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। এরপর ১২৯১ বঙ্গাব্দে ‘ভারতী’ পত্রিকায় ঘাটের কথা এবং ‘নবজীবন’ পত্রিকায় রাজপথের কথা শিরোনামে আরও দুটি ছোটগল্প ছাপা হয়। ‘মুকুট’ গল্পটি প্রথমে গল্পরূপে পাঠকদের কাছে হাজির করা হলেও পরে তা নাট্যরূপে স্থায়িত্ব পেয়েছে। সমকালীন প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথের যে কোনো লেখাকেই সমালোচকগণ তখন ‘গল্প’ বলতে নারাজ। প্রসঙ্গত, ড. সুকুমার সেন এদের যথার্থ নামকরণ করেছেন- ‘গল্প-চিত্র’।
এক.
উত্তরবঙ্গ, অধুনা বাংলাদেশের পদ্মানদীর পাড়ে গ্রামীণ জীবন-ভূমিতে রবীন্দ্র সাহিত্যে প্রথম ছোটগল্পের শুদ্ধ বুনন লক্ষ করা যায়। পদ্মা নদীর বুকের ওপর ভাসমান ক্ষুদ্র নৌকায় (বোটে) চড়ে রবিঠাকুর যখন জমিদারি দেখভালের কাজে বাংলাদেশে আসা-যাওয়া করতেন; তখনই তাঁর অন্তরে ছোটগল্পের ছোট ছোট প্লটের বিচ্ছুরণ ঘটে। বাইরের বিস্তৃত পল্লি-প্রকৃতি; নদী, মাঠ-ঘাট, ফসলের খেত আর ছোট ছোট গ্রাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে প্রচণ্ডভাবে আকর্ষণ করতে থাকে। অন্তরে সৃজন-লীলার দায় অনুভব এবং সেই দায় মুক্তির আনন্দ থেকে রবীন্দ্র সাহিত্যের এক অভিনব সৃষ্টি বাংলা ছোটগল্প। রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূগোল বাংলাদেশ। ১৮৯১ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্থায়ীভাবে ‘জমিদারি তদারকির কাজে উত্তর-পূর্ববঙ্গে ঘুরতে ঘুরতেই তিনি তাঁর ছোটগল্পের একটা বড় অংশ লেখেন। সাংস্কৃতিক আভিজাত্য এবং পারিবারিক ঐতিহ্যের এক গৌরবময় পটভূমিতে ছিল তাঁর অবস্থান।’ এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিজস্ব স্বীকারোক্তি প্রণিধানযোগ্য :
‘শিলাইদহে পদ্মার বোটে ছিলাম আমি একলা; নির্জনে নদীর বুক দিয়ে বয়ে যেত নদীর ধারারই মতো সহজে। বোট বাঁধা থাকত পদ্মার চরে। সেদিকে ধু-ধু করত দিগন্ত পর্যন্ত পাণ্ডুবর্ণ বালুরাশি জনহীন, তৃণশস্যহীন। মাঝে মাঝে জল বেঁধে আছে। সেখানে শীত ঋতুর আমন্ত্রিত জলচর পাখির দল। নদীর ওপারে গাছপালার ঘনছায়ায় গ্রামের জীবনযাত্রা। মেয়েরা জল নিয়ে যায়, ছেলেরা জলে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতার কাটে, চাষিরা গরু-মোষ নিয়ে পার হয়ে চলে অন্য তীরের চাষের খেতে, মহাজনী নৌকা গুণের টানে মন্থরগতিতে চলতে থাকে, ডিঙি নৌকা পাটকিলের রঙের পাল উড়িয়ে হু হু করে জল চিরে যায়, জেলে নৌকা জাল বাচ করতে থাকে, যেন সে কাজ নয়, যেন সে খেলা, প্রজাদের প্রাত্যহিক সুখ-দুঃখ আমার গোচরে এসে পড়ত তাদের নানা প্রকার নালিশ নিয়ে, আলোচনা নিয়ে। ... বোট ভাসিয়ে চলে যেতুম পদ্মা থেকে পাবনার কোলের ইছামতীতে, ইছামতী থেকে বাড়ালে, হুড়ো সাগরে, চলন বিলে, আত্রাইয়ে, নাগর নদীতে, যমুনা পেরিয়ে সাজাদপুরের খাল বেয়ে সাজাদপুরে। ... আমার গল্পগুচ্ছের ফসল ফলেছে আমার গ্রাম থেকে গ্রামান্তরের পথে-ফেরা এই অভিজ্ঞতার ভূমিকায়।’
 রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রসাহিত্যে ছোটগল্পের উৎস অনুসন্ধান করতে গিয়ে লিখেছেন,
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রসাহিত্যে ছোটগল্পের উৎস অনুসন্ধান করতে গিয়ে লিখেছেন,
‘রবীন্দ্রনাথ ধনী জমিদার এবং বাহিরের লোক। কাজেই তথাকার পল্লীজীবনের সঙ্গে তাঁহার অন্তরঙ্গভাবে মিশিবার উপায় ছিল না। পল্লীজীবনের মধ্যে মিলিত হইবার ইচ্ছা যতই প্রবল হোক, বাধা দুর্লঙ্ঘ; ফলে তাঁহাকে দূর হইতে, বাহির হইতে দেখিতে হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, ইহা যেন নদী-স্রোতে ভাসমান নৌকা হইতে তীরভূমির দর্শন। ইহাই সত্যকার ছোটগল্প দেখা।’
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সাহিত্যজীবনের চৌষট্টি বছরে মোট একশ উনিশটি গল্প রচনা করেছেন। ১৮৭৭ সালে প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম গল্প ‘ভিখারিণী’। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্পগুলো তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ গল্পগুচ্ছ, সে, গল্পসল্প ও তিনসঙ্গী প্রভৃতি গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কিছু গল্পে বাংলাদেশের গ্রামীণ প্রকৃতি ও জনজীবন, অপাঙ্ক্তেয় কিশোর-কিশোরীর বহুমাত্রিক রূপচিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। গল্পগুচ্ছের অনেক গল্পে জমিদার-পত্তনিদার-তালুকদার এবং নায়েব-দেওয়ান-ম্যানেজার প্রভৃতি চরিত্র অঙ্কিত হয়েছে। কিছু গল্পে ব্যবসায়ী সমাজের ছবি পাওয়া যায়। সেখানে উপস্বত্বভোগীসহ নানা পেশাজীবী মানুষের ভিড় রয়েছে। রবীন্দ্র-গল্প বিষয়ে দুটি বিভ্রান্তিমূলক মতবাদ প্রচলিত আছে। প্রথমত, রবীন্দ্রনাথের গল্পের শ্রেষ্ঠত্ব লিরিকের আবেদনে; দ্বিতীয়ত, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের জীবনের নিবিড় সংযোগ ঘটিয়ে লেখক বড় নিষ্করুণভাবে বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকেন। অভিযোগ দুটি আংশিক সত্য হলেও, পুরোপুরি সত্য নয়। কারণ, রবীন্দ্র-ছোটগল্পে চিত্রিত মানুষ ও সমাজ প্রকৃতিরঞ্জিত ও কল্পনার মিশেল থেকেই সৃষ্ট। রবীন্দ্র-গল্পে কল্পনা যদিও থাকে তবু সমাজবাস্তবতার সঙ্গে তার কোনো বিরোধ নেই, আছে অঙ্গঙ্গি হয়ে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহজ স্বীকারোক্তি-
‘অসংখ্য ছোট ছোট লিরিক লিখেছি, বোধ হয় পৃথিবীর অন্য কোনো কবি এত লেখেননি। কিন্তু আমার অবাক লাগে, তোমরা যখন বল যে, আমার গল্পগুচ্ছ গীতধর্মী। এক সময়ে ঘুরে বেড়িয়েছি বাংলার নদীতে নদীতে, দেখেছি বাংলার পল্লীর বিচিত্র জীবনযাত্রা। একটি মেয়ে নৌকো করে শ্বশুরবাড়ি চলে গেল, তার বন্ধুরা ঘাটে নাইতে নাইতে বলাবলি করতে লাগল, আহা যে পাগলাটে মেয়ে, শ্বশুরবাড়ি গিয়ে ওর কি না-জানি দশা হবে। কিম্বা ধরো একটা খ্যাপাটে ছেলে সারা গ্রাম দুষ্টুমির চোটে মাতিয়ে বেড়ায়, তাকে হঠাৎ একদিন চলে যেতে হলো শহরে তার মামার কাছে। এইটুকু চোখে দেখেছি, বাকিটা নিয়েছি কল্পনা করে। একে কি তোমরা গান জাতীয় পদার্থ বলবে? আমি বলব, আমার গল্পে বাস্তবের অভাব কখনো ঘটেনি। যা-কিছু লিখেছি, নিজে দেখেছি, মর্মে অনুভব করেছি, সে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। ... গল্পে যা লিখেছি, তার মূলে আছে আমার অভিজ্ঞতা, আমার নিজের দেখা। তাকে গীতধর্মী বললে ভুল করবে। ... ভেবে দেখলে বুঝতে পারবে, আমি যে ছোট ছোট গল্পগুলো লিখেছি, বাঙালী-সমাজের বাস্তব জীবনের ছবি তাতেই প্রথম ধরা পড়ে।’
বিবিধ দুঃখ, বেদনা, হতাশা, ক্ষোভ এসব নিয়েই আমাদের যাপিত-জীবন। জমিদার হয়েও রবিঠাকুর জীবনের দুঃখ-কষ্টগুলো মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনের নানা দুঃখ-বেদনার নির্যাস যেন তাঁর ছোটগল্প। চৌদ্দ বছর বয়সে কিশোর রবীন্দ্রনাথ, দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে প্রথম বাংলাদেশের শিলাইদহে বেড়াতে আসেন। এরপর ১৮৯৯ সালে জমিদারি তদারকি করার কাজে নিজেই আসেন এবং বসবাস করেন। ছোট নদীর ধারে সূর্য অস্ত যাওয়া আর সন্ধ্যার আকাশে তারা ওঠাকে তার মনে হয়েছে জগৎ সংসারে এক বিরল ও আশ্চর্যজনক মহৎ ঘটনা। কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি থেকে পদ্মা, ইছামতী, আত্রাই বয়ে কবি বাংলাদেশে আসতেন। বর্ষাকালের নদী প্রসঙ্গে একপত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন-
‘বর্ষার সময় খালটা থাকত জলে পূর্ণ। শুকনোর দিনে লোক চলত তার উপর দিয়ে। এ পারে ছিল একটা হাট, সেখানে বিচিত্র জনতা। দোতলার ঘর থেকে লোকালয়ের লীলা দেখতে ভালো লাগত। পদ্মায় আমার জীবনযাত্রা ছিল জনতা থেকে দূরে। নদীর চর ধু-ধু বালি, স্থানে স্থানে জলকুণ্ড ঘিরে জলচর পাখি। সেখানে যে-সব ছোট গল্প লিখেছি তার মধ্যে আছে পদ্মাতীরের আভাস। সাজাদপুরে যখন আসতুম চোখে গ্রাম্য জীবনের চিত্র, পল্লীর বিচিত্র কর্মোদ্যম। তারই প্রকাশ ‘পোস্টমাস্টার’, ‘সমাপ্তি’, ‘ছুটি’ প্রভৃতি গল্পে। তাতে লোকালয়ের খণ্ড খণ্ড চলতি দৃশ্যগুলো কল্পনার দ্বারা ভরাট করা হয়েছে।’
পোস্টমাস্টার ছোটগল্পটি রবীন্দ্র-গল্পসাহিত্যের এক অনিন্দ্য সৃষ্টি। পোস্টমাস্টার গল্পে গ্রামীণ প্রকৃতি, নদী বিশেষত পদ্মা এবং বর্ষাকালকে গল্পকার একটি অনবদ্য চরিত্র হিসেবে এঁকেছেন। ১২৯৮ সালে হিতবাদী পত্রিকায় গল্পটি প্রথম ছাপা হয়। পরবর্তীতে গল্পটি গল্পগুচ্ছে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পোস্টমাস্টার গল্পে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রতন নামের বারো-তেরো বছর বয়সের এক স্বজনহারা, অনাথ গ্রাম্য-বালিকার নিদারুণ-করুণ চিত্র এঁকেছেন। পোস্টমাস্টার একটি নিটল প্রেমের গল্প। যে প্রেম অপ্রকাশ্য ও রহস্যময়। যা কেবল হৃদয় দিয়ে অনুভব করা যায়। যার কোনো ব্যাখ্যা চলে না। এমনি এক আশ্চর্য সম্পর্কের পরিচয় পাওয়া যায় পোস্টমাস্টার গল্পের রতন ও পোস্টমাস্টার চরিত্রে। বাবা-মা, আত্মীয় পরিজনহীন রতনের ‘মনে পড়িত, তাহার একটি ছোটভাই ছিল-বহু পূর্বেকার বর্ষার দিনে একদিন একটা ডোবার ধারে দুইজনে মিলিয়া গাছের ভাঙা ডালে ছিপ করিয়া মিছামিছি মাছধরা খেলা করিয়াছিল- অনেক গুরুতর ঘটনার চেয়ে সেই কথাই তাহার মনে বেশি উদয় হইত।’ পোস্টমাস্টার গল্পের এক অনন্য চরিত্র প্রকৃতি।
‘একদিন বর্ষাকালে মেঘমুক্ত দ্বিপ্রহরে ঈষৎ-তপ্ত কোমল বাতাস দিতেছিল; রৌদ্রে ভিজা ঘাস এবং গাছপালা হইতে একপ্রকার গন্ধ উত্থিত হইতেছিল; মনে হইতেছিল যেন ক্লান্ত ধরণীর উষ্ণ নিঃশ্বাস গায়ের উপরে আসিয়া লাগিতেছে; এবং কোথাকার এক নাছোড়বান্দা পাখি তাহার একটা একটানা সুরের নালিশ সমস্ত দুপুরবেলা প্রকৃতির দরবারে অত্যন্ত করুণস্বরে বারবার আবৃত্তি করিতেছিল।’
কলকাতার নাগরিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত শহুরে লোক পোস্টমাস্টার; সদ্য চাকরিতে যোগদান করে উলাপুর নামক এক অজপাড়া গ্রামে এসে নিজেকে একদম বেমানান মনে করেন। এখানে ‘লেখকের নাগরিক টান প্রথমেই চোখে পড়ে শহুরে ছেলে পোস্টমাস্টারের চিন্তা-ভাবনায়।’ গ্রাম-বাংলার বর্ষার প্রকৃতি ও তার স্বাভাবিক ক্রিয়াকর্ম পোস্টমাস্টারের মনটিকে বড়ো করুণভাবে স্নেহকাতর করে তোলে। একা একা বসে পোস্টমাস্টার তখন দু-একটা কবিতা লেখার চেষ্টা করে। সে-সমস্ত কবিতায় যে ভাব ও ভাষা ব্যক্ত হয় তার সারমর্ম এই যে, সারা দিন তরুপল্লবের কম্পন এবং আকাশের মেঘ দেখেই যেন জীবন বড় সুখে কেটে যায়। কিন্তু এ-সব কথা পোস্টমাস্টারের মনের অগভীর প্রতিক্রিয়া। তাঁর মনের গভীর প্রতিক্রিয়া গল্পকার অনন্য আবহ সৃষ্টি করে ব্যক্ত করেছেন-
‘পোস্টমাস্টারের হাতে কাজ ছিল না- সেদিনকার বৃষ্টিধৌত মসৃণ চিক্কণ তরুপল্লবের হিল্লোল এবং পরাভূত বর্ষার ভগ্নাবশিষ্ট রৌদ্রশুভ্র স্তূপাকার মেঘস্তর বাস্তবিকই দেখিবার বিষয় ছিল; পোস্টমাস্টার তাহা দেখিতেছিলেন এবং ভাবিতেছিলেন, এই সময় কাছে একটি- কেহ নিতান্ত আপনার লোক থাকিত- হৃদয়ের সহিত একান্ত সংলগ্ন একটি স্নেহপুত্তলি মানবমূর্তি। ক্রমে মনে হইতে লাগিল, সেই পাখি ঐ কথাই বারবার বলিতেছে এবং এই জনহীন তরুচ্ছায়ানিমগ্ন মধ্যাহ্নের পল্লবমর্মরের অর্থও কতকটা ঐরূপ। কেহ বিশ্বাস করে না, এবং জানিতেও পায় না, কিন্তু ছোটপল্লীর সামান্য বেতনের সাব-পোস্টমাস্টারের মনে গভীর নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নের দীর্ঘ ছুটির দিনে এইরূপ একটা ভাবের উদয় হইয়া থাকে।’
এ গল্পে নদী এবং বর্ষাকাল যেন পোস্টমাস্টার এবং রতনের মধ্যে তৃতীয় চরিত্র হয়ে ধরা দিয়েছে। লেখক মানব জীবনের যে জটিল ও গূঢ় রহস্য সরাসরি (ভাষায়) প্রকাশ করতে পারেননি- তা প্রকৃতি তথা পদ্মা নদী ও বর্ষা-বন্দনার মাধ্যমে চমৎকারভাবে প্রকাশ করেছেন। বর্ষাকালের অনিন্দ্য বর্ণনা প্রদানের ক্ষেত্রে গল্পকার লিখেছেন, ‘শ্রাবণ মাসে বর্ষণের আর অন্ত নাই। খাল বিল নালা জলে ভরিয়া উঠিল। অহর্নিশি ভেকের ডাক এবং বৃষ্টির শব্দ। গ্রামের রাস্তায় চলাচল প্রায় একপ্রকার বন্ধ- নৌকায় করিয়া হাটে যাইতে হয়।’ নিস্তরঙ্গ পল্লি-প্রকৃতির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে না পেরে পোস্টমাস্টার একদা অসুস্থ হয়ে পড়েন।
‘এই নিতান্ত নিঃসঙ্গ প্রবাসে ঘনবর্ষায় রোগকাতর শরীরে একটুখানি সেবা পাইতে ইচ্ছা করে। তপ্ত ললাটের উপর শাঁখাপরা কোমল হস্তের স্পর্শ মনে পড়ে। এই ঘোর প্রবাসে রোগযন্ত্রণায় স্নেহময়ী নারী-রূপে জননী ও দিদি পাশে বসিয়া আছেন এই কথা মনে করিতে ইচ্ছা করে, এবং এ স্থলে প্রবাসীর মনের অভিলাষ ব্যর্থ হইল না। বালিকা রতন আর বালিকা রহিল না। সেই মুহূর্তেই সে জননীর পদ অধিকার করিয়া বসিল।’
রতন নিজে বৈদ্য ডেকে দাদাবাবুকে ঔষধ তৈরি করে খাওয়ালো। সারা রাত জেগে তার শিয়রে বসে রইলো। নিজের হাতে পথ্য রেঁধে দিলো। গভীর উদ্বেগের সঙ্গে বারবার পোস্টমাস্টারের শরীরের খোঁজখবর নিলো। এই অনাথ মেয়েটি পোস্টমাস্টারকে সেবা-শুশ্রƒষা দিয়ে সুস্থ করে তুললো। তখন পাঠকের আর বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না যে, বালিকাটি কেবল ভগ্নী বা জননীর পদ নয়, প্রেমিকার পদেও অধিষ্ঠিত হয়েছিল।
বর্ষার পল্লি-প্রকৃতির সঙ্গে রোগকাতর শরীর যেন একাকার হয়ে পোস্টমাস্টারের বদলির আয়োজন রচনা করে। কিন্তু পোস্টমাস্টারের বদলির আবেদন নামঞ্জুর হয়। ফলে চাকরিতে ইস্তফা এবং কাজে জবাব দিয়ে তিনি বাড়ি যাবার বন্দোবস্ত করেন। এমন ট্র্যাজেডিক পরিণতিতেও গল্পকার প্রকৃতির সার্থক ব্যবহার করেছেন। বর্ষার বৃষ্টি যেন হৃদয়ের কান্না হয়ে ঝরে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন- ‘অনেকক্ষণ আর কেহ কোনো কথা কহিল না। মিটমিট করিয়া প্রদীপ জ্বলিতে লাগিল এবং এক স্থানে ঘরের জীর্ণ চাল ভেদ করিয়া একটি মাটির সরার উপর টপটপ করিয়া বৃষ্টির জল পড়িতে লাগিল।’ পোস্টমাস্টারের বিদায়ের সময় ঘনিয়ে এলে রতন তার সামনে থেকে এক দৌড়ে পালিয়ে যায়। ‘পোস্টমাস্টার গল্পের জীবন-বেদনা যে কেবল দুর্ভাগিনী রতনের নয়, সর্বরিক্ত মানবতার অনিবার্য ট্র্যাজেডি-ভরাতুর।’ অজপাড়াগাঁ থেকে পোস্টমাস্টারের চলে যাওয়া রতন কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি। কারণ, পোস্টমাস্টারের বিদায়ে রতন যেন তাঁর বেঁচে থাকার একটি স্নেহপূর্ণ, আনন্দময় ও নিরাপদ আশ্রয়টুকু হারালো। ভূতপূর্ব পোস্টমাস্টার মনের মধ্যে একরাশ বেদনা নিয়ে ধীরে ধীরে নৌকার দিকে চললেন। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন-
“যখন নৌকায় উঠিলেন এবং নৌকা ছাড়িয়া দিল, বর্ষাবিস্ফারিত নদী ধরণীর উচ্ছলিত/অশ্রুরাশির মতো চারিদিকে ছলছল করিতে লাগিল, তখন হৃদয়ের মধ্যে অত্যন্ত একটা বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন- একটি সামান্য গ্রাম্য বালিকার করুণ মুখচ্ছবি যেন এক বিশ্বব্যাপী বৃহৎ অব্যক্ত মর্মব্যথা প্রকাশ করিতে লাগিল। একবার নিতান্ত ইচ্ছা হইল, ‘ফিরিয়া যাই, জগতের ক্রোড়বিচ্যুত সেই অনাথিনীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসি’- কিন্তু তখন পালে বাতাস পাইয়াছে, বর্ষার স্রোত খরতর বেগে বহিতেছে, গ্রাম অতিক্রম করিয়া নদীকূলের শ্মশান দেখা দিয়াছে- এবং নদীপ্রবাহে ভাসমান পথিকের উদাস হৃদয়ে এই তত্ত্বের উদায় হইল, জীবনে এমন কত বিচ্ছেদ, কত মৃত্যু আছে, ফিরিয়া ফল কি? পৃথিবীতে কে কাহার।”
নারী হৃদয়ের তল খুঁজে পাওয়া এত সহজ নয়। রতন পোস্টমাস্টারের সমস্ত দান প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু স্নেহপূর্ণ ভালোবাসার দান প্রত্যাখ্যান করতে পারে না। পোস্টমাস্টার চলে গেলেও নারী হৃদয়ের এক কোণে লুকিয়ে থাকা ভালোবাসা সে আর চেপে রাখতে পারে না। তাই সে অশ্রুসজল চোখে পোস্ট-অফিসের চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তার মনে হঠাৎ ক্ষীণ আশা জেগেছিল, দাদাবাবু যদি ফিরে আসে! এ প্রসঙ্গে গল্পকার লিখেছেন-
‘দাদাবাবু যদি ফিরিয়া আসে- সেই বন্ধনে পড়িয়া সে কিছুতেই দূরে যাইতে পারিতেছিল না। হায় বুদ্ধিহীন মানবহৃদয়! ভ্রান্তি কিছুতেই ঘোচে না, যুক্তিশাস্ত্রের বিধান বহু বিলম্বে মাথায় প্রবেশ করে, প্রবল প্রমাণকেও অবিশ্বাস করিয়া মিথ্যা আশাকে দুই বাহুপাশে বাঁধিয়া বুকের ভিতরে প্রাণপণে জড়াইয়া ধরা যায়।
অবশেষে একদিন সমস্ত নাড়ি কাটিয়া হৃদয়ের রক্ত শুষিয়া সে পলায়ন করে, তখন চেতনা হয় এবং দ্বিতীয় ভ্রান্তিপাশে পড়িবার জন্য চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে।’ সুভা ছোটগল্পটি রবীন্দ্র-সাহিত্যের আরেকটি বিশেষ সংযোজন। গল্পটি সাধনা পত্রিকায় পৌষ ১২৯৯ বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত হওয়ার পরে গল্পগুচ্ছে সংকলিত হয়। সুভা গল্পের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের মানসিক অবস্থা; তাদের মননচিন্তা, আবেগ ও অনুভূতির সূক্ষ্মতর দিকগুলো উপস্থাপন করেছেন। বাক্ ও শ্রবণপ্রতিবন্ধী কিশোরী মেয়ে সুভার প্রতি গল্পকারের অপরিসীম স্নেহ, হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা আর গভীর মমত্ববোধ গল্পটিকে বিশেষত্ব দান করেছে। এ-গল্পে লেখক সুভাষিণী ওরফে ‘সুভা’ নামের এক মূক-কিশোরী মেয়ের হৃদয়াভাষকে সরব করে পাঠকের সামনে উপস্থাপন করেছেন। প্রকৃতি এ-গল্পে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। ‘সুভা’ গল্পে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নদীর প্রসঙ্গটি এনেছেন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে।
‘গ্রামের নাম চণ্ডীপুর। নদীটি বাংলাদেশের একটি ছোট নদী, গৃহস্থঘরের মেয়েটির মতো; বহুদূর পর্যন্ত তাহার প্রসার নহে; নিরলসা তন্বী নদীটি আপনকূল রক্ষা করিয়া যায়; দুই ধারের গ্রামের সকলেরই সঙ্গে তাহার যেন একটা না একটা সম্পর্ক আছে। দুই ধারে লোকালয় এবং তরুচ্ছায়াঘন উচ্চতট; নিম্নতল দিয়া গ্রামলক্ষ্মী স্রোতস্বিনী আত্মবিস্মৃত দ্রুত পদক্ষেপে প্রফুল্ল হৃদয়ে আপনার অসংখ্য কল্যাণকার্যে চলিতেছে। বাণীকণ্ঠের ঘর নদীর একেবারে উপরেই। তাহার বাঁখারির বেড়া, আটচালা, গোয়ালঘর, ঢেঁকিশালা, খড়ের স্তূপ, তেঁতুলতলা, আম কাঁঠাল এবং কলার বাগান নৌকাবাহি-মাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।’ সুভা গল্পে আমরা দেখি, মানুষ যেখানে নীরব, জন্ম থেকেই যার ভাষা নেই, সেই রকম বোবা একটি মেয়ের ভাব-বিনিময়ের সংগীত হয়ে উঠেছে প্রকৃতি। ‘সেখানে সুভার মতো বোবা মেয়ের ইঙ্গিত-সংকেতই যেন প্রাকৃতিক চরিত্র হয়ে এসেছে। প্রকৃতি যেন সুভারই সংকেতধর্মী ভাষার বিশ্বব্যাপী বিস্তার। প্রকৃতির ভাষাকে মানুষের ভাষার বিস্তার হিসেবে দেখাটা অবশ্যই নতুন। শুধু প্রকৃতি নয়, ভাষাহীন প্রাণীও তার সঙ্গী ছিল। পোষা প্রাণীগুলিও সুভার আদরের ভাষা মানুষের চেয়েও সহজে বুঝতো।’ এ প্রসঙ্গে গল্পকার লিখেছেন- ‘প্রকৃতি যেন তাহার ভাষার অভাব পূরণ করিয়া দেয়। যেন তাহার হইয়া কথা কয়। নদীর কলধ্বনি, লোকের কোলাহল, মাঝির গান, পাখির ডাক, তরুর মর্মর-সমস্ত মিশিয়া চারিদিকের চলাফেরা-আন্দোলন-কম্পনের সহিত এক হইয়া সমুদ্রের তরঙ্গরাশির ন্যায় বালিকার চিরনিস্তব্ধ হৃদয়-উপকূলের নিকটে আসিয়া ভাঙিয়া ভাঙিয়া পড়ে। প্রকৃতির এই বিবিধ শব্দ এবং বিচিত্র গতি, ইহাও বোবার ভাষা-বড়ো বড়ো চক্ষুপল্লববিশিষ্ট সুভার যে ভাষা তাহারই একটা বিশ্বব্যাপী বিস্তার; ঝিল্লিরবপূর্ণ তৃণভূমি হইতে শব্দাতীত নক্ষত্রলোক পর্যন্ত কেবল ইঙ্গিত, ভঙ্গি, সংগীত, ক্রন্দন এবং দীর্ঘশ্বাস।’ ‘সুভা’ গল্পে গ্রামীণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন ও কর্ম সম্পর্কে আলোকপাত করা আছে। ঋতুপরিক্রমায় গ্রীষ্মকালে বাংলার প্রকৃতিতে একটু গরম পড়ে। তখন রোদের তাপ বেড়ে যায়। অতিরিক্ত তাপপ্রবাহে কখনো কখনো জনজীবনে নাভিশ্বাস ওঠে। তাই বিশেষ দরকার না হলে এ-সময় মানুষ ঘর থেকে বের হয় না। গল্পকার প্রকৃতির সাথে সুভাকে যেন মিলিয়ে দেখেছেন। ‘মধ্যাহ্নে যখন মাঝিরা জেলেরা খাইতে যাইত, গৃহস্থেরা ঘুমাইত, পাখিরা ডাকিত না, খেয়া নৌকা বন্ধ থাকিত, সজন জগৎ সমস্ত কাজকর্মের মাঝখানে সহসা থামিয়া গিয়া ভয়ানক বিজনমূর্তি ধারণ করিত, তখন রুদ্র মহাকাশের তলে কেবল একটি বোবা প্রকৃতি এবং একটি বোবা মেয়ে মুখোমুখি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত- একজন সুবিস্তীর্ণ রৌদ্রে, আর-একজন ক্ষুদ্র তরুচ্ছায়ায়।’ কলকাতায় সুভার বিয়ে ঠিক হয়। অনেক টাকা পণ দিয়ে সুভার বাবা বাণীকণ্ঠ মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার জন্য একটি বর জোগাড় করেন। বিয়ের জন্য তাদের সবাইকে কলকাতা যেতে হবে। কিন্তু সুভা তার চিরপরিচিত গ্রাম, পরিবার, বন্ধু প্রতাপ এবং তার মতোই বোবা দুইটি গাভি সর্বাশী ও পাঙ্গুলি এবং ছাগলছানা ও বিড়াল শাবককে ছেড়ে কিছুতেই কলকাতায় যেতে চায় না। তখন সুভার মনের অবস্থা সম্পর্কে গল্পকার লিখেছেন, ‘সেদিন শুক্লদ্বাদশীর রাত্রী। সুভা শয়নগৃহ হইতে বাহির হইয়া তাহার সেই চিরপরিচিত নদীতটে শস্যশয্যায় লুটাইয়া পড়িল- যেন ধরণীকে, এই প্রকাণ্ড মূক মানবতাকে দুই বাহুতে ধরিয়া বলিতে চাহে, ‘তুমি আমাকে যাইতে দিয়ো না, মা। আমার মতো দুটি বাহু বাড়াইয়া তুমিও আমাকে ধরিয়া রাখো।’ সুভার শারীরিক প্রতিবন্ধিতার কথা গোপন রেখে বাণীকণ্ঠ অনেক টাকা খরচ করে মেয়ে বিয়ে দিলেন বটে- তবে সংসারে বোবা মেয়ের কপালে সুখ জোটেনি। বিয়ের সাত দিনের মাথায় সব চালাকি ধরা পড়ে। সুভা যে কথা বলতে পারে না; সে আজন্ম বোবা, এ-কথা সবাই জানতে পারে; এবং তাদের বদ্ধমূল ধারণা হয় যে, সুভা যেমন বোবা তেমনি জগৎ-সংসার সম্পর্কে তার কোনো জ্ঞান নেই। ফলে, স্বামী এই অজুহাত তুলে নতুন করে আরও একটি বিয়ে করে।
‘বর পশ্চিমে কাজ করে। বিবাহের অনতিবিলম্বে স্ত্রীকে পশ্চিমে লইয়া গেল। সপ্তাহখানেকের মধ্যে সকলেই বুঝিল নববধূ বোবা। যা কেহ বুঝিল না- সেটা তাহার দোষ নহে। সে কাহাকেও প্রতারণা করে নাই। তাহার দুটি চক্ষু সকল কথাই বলিয়াছিল কিন্তু কেহ তাহা বুঝিতে পারে নাই। সে চারিদিকে চায় ভাষা পায় না যাহারা বোবার ভাষা বুঝিত সেই আজন্মপরিচিত মুখগুলি দেখিতে পায় না- বালিকার চিরনীরব হৃদয়ের মধ্যে একটা অসীম অব্যক্ত ক্রন্দন বাজিতে লাগিল- অন্তর্যামী ছাড়া আর-কেহ তাহা শুনিতে পাইল না। এবার তাহার স্বামী চক্ষু এবং কর্ণেন্দ্রিয়ের দ্বারা পরীক্ষা করিয়া এক ভাষাবিশিষ্ট কন্যা বিবাহ করিয়া আনিল।’ সুভার পরিণতি সম্পর্কে সমালোচকের মন্তব্য, ‘বোবা বালিকা সুভা পল্লীর গাছপালা পশুপাখীর সঙ্গে মিলিয়া এক রকম সুখেই ছিল, অন্তত দুঃখ কাহাকে বলে ঠিক জানিত না। এমন সময় বিবাহোপলক্ষ্যে শহরে আনিত হইয়া বোবা বালিকা সুভা এবারে সত্য সত্যই মূঢ় হইয়া পড়িল। ঐখানেই তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছে- ইহার পরে কায়িক মৃত্যু ঘটানো বাহুল্য মাত্র।’ বাংলাদেশের মানুষ, প্রকৃতি ও জনজীবনের নানামাত্রিক পরিচয় পাওয়া যায় গল্পগুচ্ছের বিভিন্ন গল্পে। একটি বিস্তৃত সময়ের প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গল্পগুলো রচনা করেছেন- যা কালে কালে বাংলার গ্রামীণ মানুষের সহজ-সুন্দর-সরল জীবনকে তুলে ধরে। পরিশীলিত ভাষা, চিত্রকল্প এবং শিল্পমহিমায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সৃষ্টির মাঝে চিরভাস্বর হয়ে রয়েছেন।