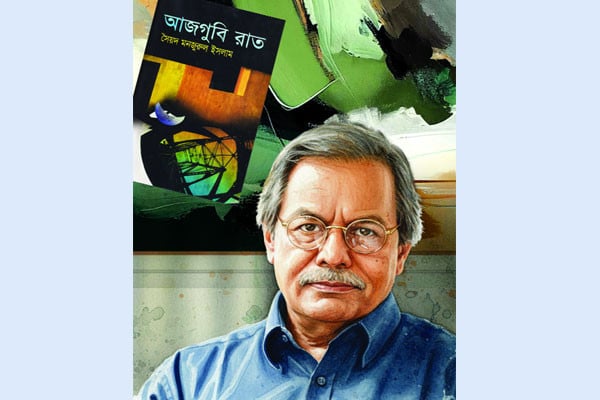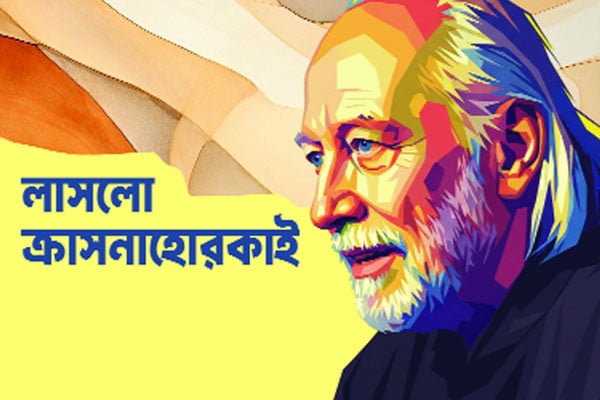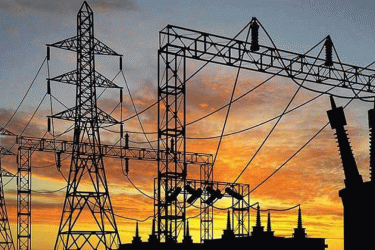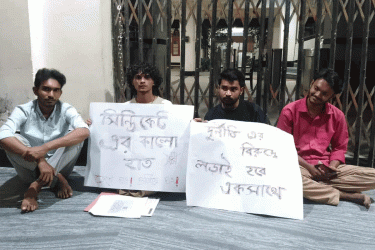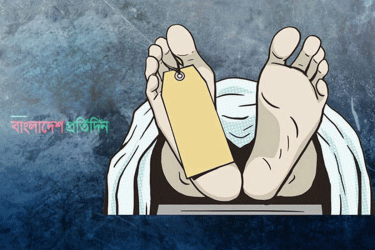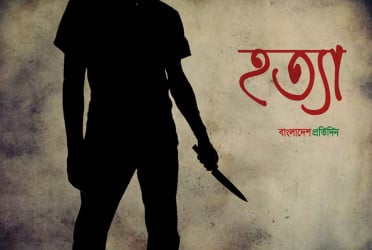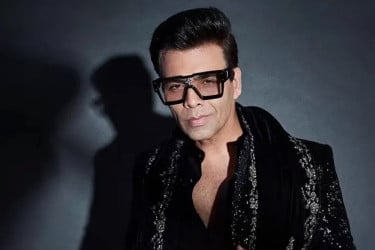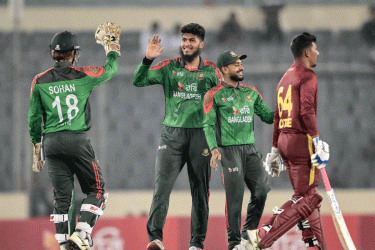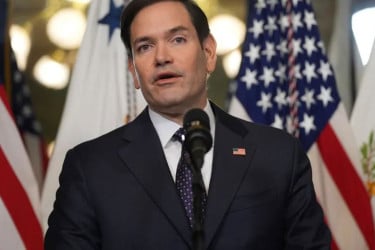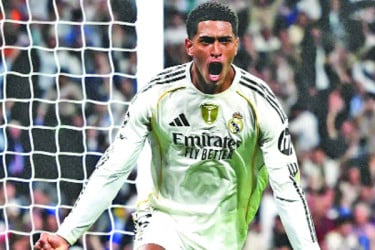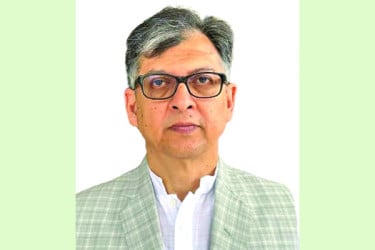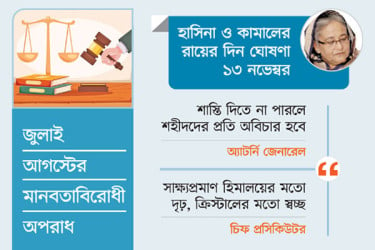কবি জীবনানন্দ দাশের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থের নাম ‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’। গ্রন্থটি পড়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিকে চিঠিতে জানিয়েছিলেন “তোমার কবিতাগুলি পড়ে খুসি হয়েছি। তোমার লেখায় রস আছে, স্বকীয়তা আছে এবং তাকিয়ে দেখার আনন্দ আছে।”
এর আগে জীবনানন্দ তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ‘ঝরাপালক’ (১৯২৮) পাঠিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথকে। কবিকে লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ- “তোমার কবিত্বশক্তি আছে তাতে সন্দেহ মাত্র নেই। কিন্তু ভাষা প্রভৃতি নিয়ে এত জবরদস্তি কর কেন বুঝতে পারিনে। কাব্যের মুদ্রাদোষটা ওস্তাদীকে পরিহসিত করে।
ুবড়ো জাতের রচনার মধ্যে একটা শান্তি আছে, যেখানে তার ব্যাঘাত দেখি সেখানে স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মে। জোর দেখানো যে জোরের প্রমাণ তা নয় বরঞ্চ উলটো।”
জীবনানন্দ তার উত্তরে দীর্ঘ চিঠি লিখেছিলেন, সেটি সম্ভবত রবীন্দ্রনাথকে পাঠানো হয়নি।
জীবনানন্দ দাশের প্রয়াণের পর পরই কবি নরেশ গুহ যে স্মৃতিচারণা করেছেন, তার মধ্যেও আমরা চকিত মূল্যায়নের আভাস পাই। নরেশ গুহ লিখেছেন, “... তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর পরে তখন দেশ তাঁকে স্বীকার করলো। শুধু কলকাতা শহরে নয়, যাকে আমরা মফস্বল বলি, যে কোনো সজীব আন্দোলনের ঢেউ যেখানে গিয়ে পৌঁছাতে পৌঁছাতে এক যুগ অন্তত কেটে যায়, সেই সব ছোট শহর, আধা শহর, পল্লীগ্রাম, এমনকি প্রবাসী বাংলা সমাজেও তাঁর স্মরণসভার অসংখ্য অনুষ্ঠান হয়েছে। ‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’র প্রথম সংস্করণ শেষ হতে অন্তত পনেরো বছর লেগেছিলো, ‘বনলতা সেন’-এর দু’বছর লাগলো না। দেখে একদিকে যেমন আনন্দ হয়, অন্যদিকে তেমনি এই ভেবে বিষণ্ন বোধ করি যে, বেঁচে থাকতে তাঁকে কত বড়ো অনাদরই সহ্য করতে হয়েছে। প্রতিভার প্রতি এই একনিষ্ঠ প্রাথমিক বৈরিতা হয়তো শুধু বাংলাদেশেরই চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য নয়। কিন্তু সে কথা ভেবে আত্মদোষের লাঘবও কিছু হয় না।
কবি জীবনানন্দ দাশের প্রতি পিশুনদের আক্রমণ অস্বাভাবিক তীব্র হয়ে উঠেছিলো, তার কারণ আমাদের অনভ্যস্ত ছন্দ প্রকরণে এমন প্রবল কাব্যস্রোত তিনি বইয়ে দিলেন যে, বধির হয়ে তাকে উপেক্ষা করাও অসম্ভব ছিলো। অক্ষমকে আমরা উপেক্ষা করতে পারি, আর যিনি শক্তিমান তাঁকে প্রথমে অশ্রদ্ধা করি, অবিশ্বাস করি, নিন্দা করি, তারপর সমাদরে গ্রহণ করতে বাধ্য হই। মৃত্যুর শোক চিরকাল থাকে না, এবং অসম্ভব ক্ষতির সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু আমাদের কিছু পূরণও করে। জীবনানন্দের আকস্মিক শোচনীয় মৃত্যুর পরে তাঁর কাব্যের এবং সাধারণভাবে আধুনিক বাংলাকাব্যের প্রতি বৃহৎ বাঙালি পাঠকসমাজের অনীহা যদি কিছুটা পরিমাণেও দূর হয়ে থাকে-মৃত্যুর শীতল হাত থেকে সেই দানটুকুই আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করবো।...
জগদীশ ভট্টাচার্য তাঁর দীর্ঘ রচনায় জীবনানন্দ দাশের কাব্যচারিত্র্যের নানা দিক উন্মোচন, বিশ্লেষণ, অবলোকন ও পর্যবেক্ষণ করেছেন (সূত্র : সুব্রত রুদ্র সম্পাদিত জীবনানন্দ : জীবন আর সৃষ্টি, নাথ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৯)। তিনি লিখেছেন, “...ভাষা সৃষ্টির ক্ষেত্রে জীবনানন্দের কবিদৃষ্টির স্বাতন্ত্র্যই প্রথমে লক্ষ করবার মতো। এই বিশ্বভুবনকে-এই নিসর্গলোকের রূপ-রং-শব্দ-গন্ধকে তিনি নিজের ইন্দ্রিয় ও মন দিয়ে নিজের মতো করে অনুভব করেছেন। তার ফলে আমাদের এই চিরপরিচিত জগৎ প্রথমে কবির একান্ত নিজস্ব একটি মনোজগতে রূপান্তরিত হয়ে, তাঁর কলাকৃতিতে সম্পূর্ণ নতুন রূপ নিয়ে, আমাদের কাছে ফিরে এসেছে। বাংলা সৌন্দর্যালংকৃত কবিভাষার সৃষ্টিতে ভারতচন্দ্রের পরে মধুসূদনের কৃতিত্ব অসাধারণ। তারপর রবীন্দ্রনাথের হাতে সে ভাষা রূপের জগৎ ও সুরের জগতে নব নব বর্ণবৈভব ও ধ্বনিমাধুর্যে ষড়ৈশ্বর্যময়ী হয়ে উঠেছে। জীবনানন্দের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব এই যে, রবীন্দ্রনাথের বাণীবিশ্বের অধিবাসী হয়েও তিনি আরেকটি বাণীবিশ্ব রচনা করে যেতে পেরেছেন।...
হাওড়া গার্লস কলেজের ইংরেজি বিভাগে একসময় অধ্যাপনা করেছেন কবি জীবনানন্দ দাশ। তাঁর সহকর্মী ছিলেন অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (বাংলা বিভাগের প্রধান)। চাকরিজীবন কেমন ছিল কবির? প্রিয় সহকর্মীর স্মৃতিচারণা-
“একদিন অধ্যক্ষ বিজয় বাবু এসে বললেন, ইংরেজি বিভাগে একজন নতুন অধ্যাপক আসছেন। তাঁর নাম জীবনানন্দ দাশ। শুনেই আমরা বিস্মিত হয়ে কবি জীবনানন্দের আবির্ভাবের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। তখন ‘নাভানা’ থেকে তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতার সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। সে সময়ে তিনি যথেষ্ট পরিচিত, সুখ্যাত এবং বিতর্কিতও বটে।
‘শনিবারের চিঠি’তে প্রায় প্রতি সংখ্যায় তাঁকে ব্যঙ্গ-বিদ্রƒপ করা হতো। কারণ তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু, রচনা ভঙ্গিমা ও তাৎপর্য খুবই অদ্ভুত এবং উদ্ভট বলে মনে হয়েছিল।
যাই হোক, তিনি চাকরিতে যোগদান করলেন। ইতিপূর্বে দেশভাগ হয়েছে। স্বাধীনতা এসেছে এবং পূর্ববঙ্গ থেকে দলে দলে বাস্তুহারা সাধারণ ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় কলকাতায় মাথা গোঁজার ঠাঁই খুঁজছিলেন। জীবনানন্দ পূর্ববঙ্গের কলেজ ছেড়ে কলকাতায় এলেন-একটি মফস্বল কলেজে যোগ দিয়ে কোন প্রকারে পায়ের তলায় মাটি খুঁজছিলেন।
সেই তিনি গার্লস কলেজে বিনা আবেদনে অধ্যাপনায় কৃত হলেন, এবং শুধু অধ্যাপক নন, একেবারেই ইংরেজি বিভাগের প্রধান হয়েই যোগদান করলেন। অধ্যক্ষ বিজয়কৃষ্ণের মানুষ চিনবার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। তিনি সহজেই জীবনানন্দের প্রতিভা বুঝতে পেরেছিলেন। ইতিপূর্বে রুচি-বিরোধী কবিতা লেখার অপরাধে ব্রাহ্ম নেত্রীদের সহযোগিতায় গড়ে ওঠা সিটি কলেজের চাকরি খোয়ালেন। পরে পূর্ববঙ্গের দু’একটি কলেজে যোগ দিলেন, কিন্তু অধ্যাপক হিসেবে বিশেষ খ্যাতি লাভ করতে পারেননি। তবে হাওড়া গার্লস কলেজের ছাত্রীদের কাছ থেকে প্রচুর শ্রদ্ধা পেয়েছিলেন। তিনি ইংরেজি গদ্য প্রবন্ধ পড়াতেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংকলিত সেই গদ্যগ্রন্থটি অতিশয় নীরস। কিন্তু ছাত্রীদের কাছে শুনেছি নীরস গদ্যও নাকি তাঁর পড়ানোর গুণে কবিতার মতো স্বাদু হয়ে উঠতো।
প্রথমদিনের কথা বলি। আমরা সকলে আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম। অধ্যক্ষ মহাশয় এক নতুন অধ্যাপককে সঙ্গে নিয়ে আমাদের ঘরে এলেন এবং পরিচয় করিয়ে দিলেন। সাদা ধুতি পাঞ্জাবি পরা একজন মধ্যবয়সি বাঙালি ভদ্রলোক। একটি চক্ষু একটু ট্যারা মতো। অত্যন্ত কম কথা বলেন। মৃদু হাসি ও নমস্কার বিনিময়ের পর তাঁকে আমরা অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করলাম।
বেশি কথা বলতেন না বলে বোধহয় সহজেই অন্তরঙ্গ হতে পারতেন। সকলে মিলে চা খাওয়া হতো, অধ্যাপিকা বিনিতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার সঙ্গে আড্ডা জুড়ে দিতেন। বলতেন- কবি, আপনার কাপ থেকে একটু চা আমার ডিশে ঢেলে দিন। তিনি সকৌতুকে চোখ তুলে বলতেন, কেন? বিনিতা বলতেন, হয়তো এমন দিন আসতে পারে যে দিন আমি সকলের কাছে গর্ব করতে পারবো, জীবনানন্দ তাঁর কাপ থেকে আমাকে চা ঢেলে দিয়েছিলেন। শুনেই তিনি অট্টহাস্য করে উঠতেন, কিন্তু সে বড় মজার হাসি। সমস্ত চোখ-মুখ হেসে উঠতো। কিন্তু কোনো শব্দ ছিল না -যাকে বলে শব্দহীন অট্টহাস্য।”
কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’ শিরোনামে স্মৃতিচারণা করেছেন কবি জীবনানন্দ দাশের। তাঁর লেখা থেকে উদ্ধৃতি-
“... জীবনানন্দ ছিলেন ষোলআনা শুদ্ধ একজন কবি। তাঁর মানসিক গঠনের যে যৎসামান্য পরিয়ে আমরা পেয়েছিলুম, তাতে মনে হতো, তিনি যে কবিতা লেখেন, এটাই ছিল তার একমাত্র পরিচয়। বস্তুত, কবিতা ছাড়া জাগতিক অন্য কোনও ভাবনার ধারই সম্ভবত তিনি ধারতেন না। এমন মানুষের পক্ষে অন্যবিধ কোনও কাজই বিশেষ স্বস্তিকর হবার কথা নয়। এমনকি, বরিশালে তিনি যে অধ্যাপনার কাজ করতেন, তাও হয়তো তার কাছে খুব স্বস্তিকর ঠেকেনি। সেক্ষেত্রে সাংবাদিকতা নামক বৃত্তিটি যে তার কাছে আরও অস্বস্তিকর হয়ে দাঁড়াবে, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।
কিন্তু যিনি শুদ্ধতম কবি, তাঁকেও তো জীবন ধারণ করতে হয়, সংসার প্রতিপালন করতে হয়। বাড়িভাড়া গুনতে হয়, জামাকাপড় কিনতে হয়, মুদির প্রাপ্য মেটাতে হয়। এটা তো কালিদাসের কাল নয় যে, স্রেফ কবিতা লেখার সুবাদেই ‘উজ্জয়িনীর বিজন প্রান্তে কানন ঘেরা বাড়ি’ কিছু নিষ্কর জমি ও মোটা অংকের মাসোহারার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। এ কালে, বিত্তশালী পরিবারের সন্তান না হলে, যা-হোক একটা চাকরি-বাকরি করতে হয় কবিকেও। বেঁচেবর্তে থাকার এই যে শর্ত, জীবনানন্দের মতো আদ্যন্ত কবিও এ থেকে রেহাই পাননি।
...‘স্বরাজ’-এ খুব বেশি দিন ছিলেন না জীবনানন্দ। কিন্তু তাঁর স্বল্পায়ু জীবনের যে একটা ক্ষুদ্র অংশ তিনি ওখানে কাটিয়ে যান, তাও যে মোটেই সুখে কিংবা স্বস্তিতে কাটেনি, এটা না বললে সত্য গোপন করা হয়। আসলে খবরের কাগজের জগতে সফল হওয়ার জন্যে যে একটা ‘এই এখুনি করে দিচ্ছি’ গোছের চটপটে ভাব ও লোক ভোলানো স্মার্টনেসের দরকার হয়, তার মতন ধীরস্থির ও চিন্তাশীল মানুষের চরিত্রে তা থাকা সম্ভব নয়, ছিলও না। ফলে দু’চার দিনের মধ্যেই রটে যায় যে, রবিবাসরীয় বিভাগের সম্পাদক হিসেবে তিনি একেবারেই অযোগ্য। সব আপিসেই কিছু-না-কিছু স্থূল প্রকৃতির মানুষ থাকে, ‘স্বরাজ’-এও ছিল, সম্ভবত তারাই সেখানে ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। জীবনানন্দের জীবনকে তারা অতিষ্ঠ করে তোলে। তাকে লক্ষ্য করে ছুড়তে থাকে চোখা-চোখা বিদ্রƒপের বাণ।
জীবনানন্দ সবই বুঝতে পারতেন। সংবেদনশীল, সূক্ষ্ম অনুভূতির মানুষ বলে প্রতিকূল পরিবেশের বেদনাও নিশ্চয়, আর পাঁচজনের তুলনায়, তার বুকে আরও বেশি করে বাজত। কিন্তু মুখে তিনি কিছুই বলতেন না। শুধু যে সপ্তাহ আমার দুপুরের শিফটে ডিউটি থাকত, চারটে নাগাদ নিজের টেবিল ছেড়ে উঠে আসতেন আমার টেবিলের কাছে। বলতেন, ‘চলুন, বেরিয়ে পড়া যাক।’ আমার তো পাঁচটা পর্যন্ত কাজ করার কথা। কিন্তু তা আর করা হতো না। তাঁর মুখের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারতুম যে, তিনি আর পেরে উঠছেন না, এখানে নিঃশ্বাস নিতেই কষ্ট হচ্ছে। হাতের কাজ অন্যকে বুঝিয়ে দিয়ে তৎক্ষণাৎ উঠে পড়তুম। বলতুম, ‘চলুন।’
ক্রিক রো দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ওয়েলিংটন স্কোয়ার। ট্রাম রাস্তা পেরিয়ে আরও খানিক হাঁটলে, বাঁ দিকে ‘পূর্বাশা’ পত্রিকার অফিস। সারাটা পথ কথা বলতেন। বরিশালের কথা। বাংলার ভূপ্রকৃতি আর গাছপালার কথা। নদীর কথা। পাখির কথা। এতক্ষণ তো জেলখানায় বন্দি হয়ে ছিলেন, পারতপক্ষে কথা বলেননি। বুঝতে পারতুম যে, সেই না-বলা কথাগুলিই এবার বেরিয়ে আসছে। ‘পূর্বাশা’ আপিসে বসে কথা বলতে বলতে সন্ধ্যে হয়ে যেত। তারপর যখন কথা শেষ হতো, তখন সঞ্জয়দাই বলতেন, যাও নীরেন, ওঁকে বালিগঞ্জের বাসে তুলে দিয়ে এসো।’
‘স্বরাজ’ পত্রিকায় যারা তাঁকে নিয়ে ব্যঙ্গবিদ্রƒপ করত, “তাদের জানবার কথা নয় যে, জীবনানন্দ একদিন ওখানে কাজ করেছিলেন বলেই কাগজখানার নাম আজও আমরা মনে রেখেছি। নইলে কবেই ভুলে যেতুম।”
কবি সমালোচক বুদ্ধদেব বসুর তাঁর স্মৃতিকথাটি রচিত হয় জীবনানন্দ দাশের প্রয়াণের পরের বছর, ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে। বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন,
“... যৌবনে, যখন মানুষের মন স্বভাবতই সম্প্রসারণ খোঁজে, আর কবির মন বিশ্বজীবনে যোগ দিতে চায়, সকলের সঙ্গে মিলতে চায় আর সকলের মধ্যে বিলিয়ে দিতে যায় নিজেকে, সেই নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের ঋতুতেও তিনি বুঝেছেন যে তার গান জীবনের ‘উৎসবের’ বা ‘ব্যর্থতার নয়, অর্থাৎ বিদ্রোহের, আলোড়নের নয়-তার গান সমর্পণের আত্মসমর্পণের, স্থিরতার।
‘পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত’ রোমান্টিক হয়েও তাই তিনি ভাবের দিক থেকে রোমান্টিকের উল্টো, আধুনিক বাংলা কাব্যের বিচিত্র বিদ্রোহের মধ্যে তাঁকে আমরা দেখতে পাই না। বস্তুত তাঁকে যেন বাংলা কাব্যের মধ্যে আকস্মিকরূপে উদ্ভূত বলে মনে হয়, সত্যেন্দ্রনাথ ও নজরুল ইসলামের ক্ষণিকের প্রভাবের কথা বাদ দিলে- তিনি যে মহাভারত থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত প্রবাহিত তাঁর পূর্বজ স্বদেশীয় সাহিত্যের কোনো অংশের দ্বারা কখনো সংক্রমিত হয়েছিলেন, বা কোনো পূর্বসূরির সঙ্গে তার একাত্মবোধ জন্মেছিলো, এমন কোনো প্রত্যক্ষ পরিচয় তাঁর কাব্যে নেই বললেই চলে।
এ থেকে এমন কথাও মনে হতে পারে যে, তিনি বাংলা কাব্যের ঐতিহ্যস্রোতের মধ্যে একটি মায়াবী দ্বীপের মতো বিচ্ছিন্ন ও উজ্জ্বল, এবং বলা যেতে পারে যে, তার কাব্যরীতি-হুতোম অথবা অবনীন্দ্রনাথের গদ্যের মতো একবারেই তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিগত, তারই মধ্যে আবদ্ধ, অন্য লেখকের পক্ষে সেই রীতির অনুসরণ, অনুশীলন বা পরিবর্ধন সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে এ বিষয়েও সন্দেহ নেই যে চলতিকালের কাব্যরচনার ধারাকে তিনি গভীরভাবে স্পর্শ করেছেন, সমকালীন ও পরবর্তী কবিদের উপর তাঁর প্রভাব কোথাও কোথাও এমন সূক্ষ্মভাবে সফল হয়ে উঠেছে যে, বাইরে থেকে হঠাৎ দেখে চেনা যায় না। বাংলা কাব্যের ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর আসনটি ঠিক কোথায় সে বিষয়ে এখনই মনস্থির করা সম্ভব নয়, তার কোনো প্রয়োজনও নেই এই মুুহূর্তে। এই কাজের দায়িত্ব আমরা তুলে দিতে পারি আমাদের ঈর্ষাভাজন সেই সব নাবালকের হাতে, যারা আজ প্রথমবার জীবনানন্দের স্বাদুতাময় আলো-অন্ধকারে অবগাহন করছে। আপাতত, আমাদের পক্ষে এই কথাই কৃতজ্ঞচিত্তে স্মর্তব্য যে, ‘যুগের সঞ্চিত পণ্যের’ অগ্নিপরিধির মধ্যে দাঁড়িয়ে যিনি ‘দেবদারু গাছে কিন্নরকণ্ঠ’ শুনেছিলেন, তিনি এই উদ্ভ্রান্ত বিশৃঙ্খল যুগে ধ্যানী কবির উদাহরণস্বরূপ।
অর্থাৎ এক হিশেবে তিনি বাংলা কাব্যের প্রথম খাঁটি আধুনিক।